হাওর বার্তা ডেস্কঃ ভারতীয় জ্বালানি ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ। পড়ালেখা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক এবং কম্পিউটার সায়েন্স ও অপারেশন রিসার্চে স্নাতকোত্তর। দায়িত্ব পালন করছেন ইন্ডিয়া পিপলস সায়েন্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। কর্মরত রয়েছেন বিয়ন্ড কোপেনহেগেন কালেক্টিভসের এনার্জি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্রুপের আহ্বায়ক হিসেবেও। ২০০৯ থেকে ২০১৪ অবধি সদস্য ছিলেন ভারতের ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব অ্যান্টিনিউক্লিয়ার মুভমেন্টসের। কাজের ক্ষেত্র জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন, পানি ও পরিবেশগত জটিল ইস্যু। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (আরআইবি) আয়োজিত ‘জলবায়ুসহিষ্ণু কৃষি ও এর বিকল্প’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে সম্প্রতি ঢাকায় এসেছিলেন তিনি। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে বাংলাদেশের করণীয়, ভারতের অভিজ্ঞতা, দূষণ, উন্নয়ন, জ্বালানি, কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরূপ প্রভাব, বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় কথা বলেন একটি জাতীয় দৈনিকের সঙ্গে। তা হুবহু তুলে ধরা হলো-
জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিতে থাকা ওপরের সারির দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। ঝুঁকি মোকাবেলায় কী করতে পারে বাংলাদেশ?
ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ একা কী করতে পারে এবং বাকি দেশগুলোর সাহায্যে কী করা যায়— দুই রকম বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তন প্রধানত দুটো ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে, যাকে আমরা হাইড্রো-মেটিওরোলজিক্যাল ডিজাস্টার বলি। এক. বড় ঝড় আর দুই. বন্যা হওয়া। এ দুটি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, যা বিভিন্ন তথ্যে দৃশ্যমান। তার মানে, এ দুটোর জন্য তৈরি হতে হবে। বাংলাদেশের একটি বড় অংশ উপকূলীয় অঞ্চল হওয়ায় ব্যাপক ঝড়প্রবণ এবং আরেকটি বড় অঞ্চল নদীভিত্তিক হওয়ায় প্রচণ্ড বন্যাপ্রবণ। কাজেই বাংলাদেশকে সমুদ্র উপকূল থেকে আসা ঝড় এবং ওপর থেকে আসা বন্যার পানি (হোক সেটা বাংলাদেশের অভ্যন্তর কিংবা ভারত থেকে আসা পানি) থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে। এর কারণে শুধু সেতু বা কিছু অবকাঠামো নয়, প্রচুর চাষের জমি ও মত্স্যসম্পদের ক্ষতি হয়। সুতরাং বাঁচানো মানে শুধুই ব্যয়বহুল বড় বড় অবকাঠামো নয়, সাধারণ মানুষের ছোট অবকাঠামোও বাঁচাতে হবে। এ বিষয়ের ওপর বেশি জোর দিতে হবে, সেটি বাংলাদেশের নিজের তরফ থেকে।
পরিসংখ্যান বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনে হাইতির পর বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংকের শ্রেণীকরণ দেখুন। তারা পাঁচটি ক্যাটাগরি করেছে। তাতে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা ১২টি দেশের মধ্যে তিনটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ রয়েছে। তার ওপর বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি), হাতে অর্থকড়ি কম। কাজেই বাংলাদেশকে এ অবস্থানও ছাড়লে চলবে না যে, চলমান সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থ বা অন্য যেকোনো সাহায্য দিতে জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ী দেশগুলোর নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্ব অবশ্যই তাদের পালন করতে হবে। এটা প্যারিস চুক্তিতে খুব পরিষ্কারভাবে লেখা নেই, যেটি কিয়োটো প্রটোকলে কিছুটা হলেও ছিল। কিন্তু ম্যাকানিজমগুলো রয়েছে। যেমন— আগে বাংলাদেশের জন্য ছোট দুটি ডেডিকেটেড ক্লাইমেট ফান্ড ছিল, যেখান থেকে অর্থ পেত। এখন যেমন গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এসেছে। সবাই বলছে, এটি সবচেয়ে বড় ফান্ড হবে। যদি তাদের কথা বা প্রতিশ্রুতিমতো ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রতি বছর দেয় ২০২০ সাল থেকে, তাহলে সেটি বিশ্বব্যাংকের সাহায্যের দ্বিগুণ হবে। সেখানে নিজের এবং একই ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর কাছে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স তৈরিতে অর্থ পৌঁছাতে বাংলাদেশকে একটি ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক চাপ রাখতে হবে।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ভারতের অভিজ্ঞতাটা কেমন?
ভারতের অভিজ্ঞতাটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে। কারণ ভারতে বর্তমানে এ-সম্পর্কিত প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। যেমন— আমাদের আইএনসিসিএর (ইন্ডিয়া নেটওয়ার্ক ফর ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ অ্যাসেসমেন্ট) ‘ফোর বাই ফোর’ নামে একটি মূল্যায়নধর্মী গবেষণাপত্র আছে। তারপর বেশকিছু জায়গায় পানি, চাষী, ফসলি জমিতে কী ধরনের প্রভাব পড়ছে, সেটি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। খুব যে ব্যাপক মাত্রায় হচ্ছে বা প্রত্যেক ছোট ভূখণ্ডভিত্তিক প্রভাব জানা যাচ্ছে তা নয়, কিন্তু একটি মোটামুটি আইডিয়া রয়েছে। দুটি উদাহরণ দিই। ২০১৫ সালে ভারতের বড় একটি অংশে শুখা (খরা) হয়েছিল। অ্যাসোচ্যামের (ভারতের অন্যতম পুরনো বাণিজ্য ও শিল্প সংঘ) হিসাব অনুসারে, শুধু ২০১৫ সালে ওই ধরনের এক ঘটনায় সর্বভারতে সার্বিকভাবে প্রভাব পড়েছিল ১০০ বিলিয়ন ডলারের মতো, যেটি ভারতের জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ। খরার ঘটনায় একটি দেশের জিডিপির ৫ শতাংশ ক্ষতি মানে বিশাল ব্যাপার। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, ওই খরায় ভারতে ৩২ কোটি ছোট, মধ্যম ও প্রান্তিক চাষীর ৫০-৭০ শতাংশ আয় নষ্ট হয়ে যায়। তাদের জন্য সেটা বাঁচা-মরার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কতটা গভীরতর, সেটা সহজেই অনুমেয়।
বাংলাদেশের দিক থেকে অপরিকল্পিত শিল্পায়নে একদিকে নদ-নদী দূষিত হচ্ছে, আবার উজানে ভারতীয় অংশেও পানি বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে। ফলে পুরো জলজ জীবন হুমকিতে পড়ছে। এক্ষেত্রে যৌথভাবে কী করা যেতে পারে?
যৌথভাবে এখানে কাজ করার অনেক ক্ষেত্র আছে। আর তা করতে না পারলে সামগ্রিকভাবে অনেক ক্ষতি হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল এভাবে আলাদা হয়ে থাকতে পারব না। দক্ষিণ এশিয়ায় দুটি বিষয় আমাদের একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে। এক. হিমালয় এবং দুই. তিনটি সাগর— ভারত মহাসাগরের সঙ্গে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন, বর্ষা, শুখা, ঝড় কিংবা হাওয়া চলা যা-ই বলুন না কেন, তা ট্রান্স-হিমালয়ান প্লেট এবং তিন সাগর মিলে হয়। এ তিনটির ইন্টারঅ্যাকশনে এ অঞ্চলের জলবায়ু খুব নিয়ন্ত্রিত। তার সঙ্গে এল-নিনোর মতো প্যাসিফিকের কিছু আছে বটে, কিন্তু লোকালি এ দুটো বিষয় পুরো সাত-আটটি দেশকে বেঁধে রেখেছে। তার মানে পুরো উপমহাদেশটা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কাজেই ভারত যেহেতু উজানের দেশ, সেহেতু ভারতের একটি দায়িত্ব আছে— পানি কি শুধু আমরাই নেব? কখনো কখনো ভারতের নেতারা উল্টো আচরণ করেছেন, কখনো কখনো একটু জিম্মাদারিও দেখিয়েছেন। যাদের (পাকিস্তান) সঙ্গে এত সংঘাত, তাদের সঙ্গে সিন্ধু চুক্তি এখন অবধি চলতে পারে, তাহলে বাংলাদেশের সঙ্গে কেন চলতে পারবে না। আমাদের সঙ্গে তো বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ। দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে কিছু উত্তেজনা আছে কিন্তু বাকি সম্পর্ক ভালো। এ অবস্থায় আন্তঃনদীগুলোর পানির একটি যুক্তিযুক্ত ভাগাভাগি হওয়া জরুরি। কারণ ফার্স্ট ইউজার প্রিন্সিপাল বিবেচনা করলে দেখা যাবে, ওইসব নদীর পানিতে বাংলাদেশের মানুষের অধিকার রয়েছে।
দূষণ রোধে যৌথভাবে কী করা যায়?
পানি ভাগাভাগি করা অনেক কঠিন। দূষণ কম করা অনেক সোজা। সব জায়গায় এমিশন রুলস আছে যে, লিকুইড ডিসচার্জ একটি ইটিপিতে ট্রিটমেন্ট করে ছাড়তে হবে। নদীতে সরাসরি ছাড়ার নিয়ম নেই। সেটা করা হয় অবৈধভাবে। এক্ষেত্রে পলিউশন এমিশন কন্ট্রোল মনিটরিং এবং লোকাল ইনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলো কাজ করছে না। তাদের কাজ করানো খুব একটা কঠিন নয়। নির্দিষ্ট বিভাগ, জনবল, কারিগরি সক্ষমতা, সরঞ্জাম সবই আছে। ওপর থেকে চাপ দেয়া হোক যে, র্যানডম চেক করতে হবে; না হলে শোকজ নোটিস বা চাকরি যাবে। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে বিষয়টি আরেকটু গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে আন্তঃসীমান্ত ইস্যু রয়েছে। নির্দিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা ভারতে করাই যায়। তবে বাংলাদেশের মামলা করার বিষয়টি নিয়ে একটু ধাঁধা আছে, কীভাবে করা হবে। বাংলাদেশের কোনো জনগোষ্ঠী যদি বলে, উপরের দূষণের কারণে আমাদের তিস্তা বা অন্য যেকোনো নদীর মাছ এত কমে গেছে বা আমাদের বিভিন্ন অসুখ হয়েছে। অতএব আমরা ভুক্তভোগী। সেটা বাংলাদেশ লিগ্যালি চ্যালেঞ্জ করতে পারবে কিনা, ভারতীয় কোর্ট কীভাবে নেবে, সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, ওই পর্যায়ে যাওয়ার আগেই রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর জরুরি পদক্ষেপ নেয়া উচিত। ভারতের অনেক বেসরকারি এজেন্সি (এনজিও) বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। কিন্তু গ্যাপ (ব্যবধান) রয়েছে সরকারি এজেন্সিগুলোর পর্যায়ে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যদি ভারতকে বলে এবং ভারত সরকারও যদি উদ্যোগ নেয়, তাহলে দূষণ বন্ধ অনেক সহজ।
এবার আসা যাক জ্বালানি প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের মতো দেশে উন্নয়ন ও জ্বালানির মূল তর্কটা কী?
আমরা সবাই চাই উন্নয়ন। আমরা বিদ্যুৎ তো বিদ্যুতের জন্য চাই না। বিদ্যুৎ বা বাকি জ্বালানি একটি সেবা (সার্ভিস)। আর এ সেবা মানুষের জীবনমান উন্নত করার জন্যই। জীবনমান পরিমাপের কিছু মানদণ্ড রয়েছে। এর মধ্যে এখন অবধি সর্বজনগ্রাহ্য একটি মানদণ্ড হলো, মানব উন্নয়ন সূচক (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স)। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে— এ অঞ্চলের বেশকিছু দেশ ভারতের চেয়ে অনেক কম জ্বালানি নিয়ে মানব উন্নয়ন সূচকে এগিয়ে আছে। যেমন— শ্রীলংকা। দেশটিতে প্রতি বছর বিদ্যুতের খরচ ভারতের ব্যক্তিপ্রতি বিদ্যুতের খরচের তুলনায় ৬০ শতাংশ মাত্র। ভারতের যেমন ৮০০ ইউনিট, শ্রীলংকায় ৪৯০ ইউনিট মাত্র। অনেক কম। কিন্তু শ্রীলংকার মানব উন্নয়ন সূচক হলো, দশমিক ৭১৫। যেটি উচ্চ মানব উন্নয়ন সূচকেরই স্মারক। আর আমাদের ভারতের মানব উন্নয়ন সূচক হলো দশমিক ৬০৯। মানে আমরা নিম্ন থেকে মধ্যম পর্যায়ে গিয়েছি।
বাংলাদেশ কিন্তু ভারতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে রয়েছে। কারণ ব্যক্তিপ্রতি ৩০০ ইউনিটের বিদ্যুৎ খরচ করে বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচক দশমিক ৫৫৬-এর মতো। এখন বাংলাদেশকে নীতি গ্রহণ করতে হবে বিদ্যুৎ বা অন্য জ্বালানি সত্যিকার মানব বিকাশের কাজে লাগাবে নাকি বড় বড় শপিংমল করবে, যেখানে প্রচুর বিদ্যুৎ লাগে। গ্যাস, তেল, কয়লা, পারমাণবিক শক্তি বা সোলার— যা দিয়েই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হোক না কেন, প্রতিটিরই আলাদা আলাদা ব্যয় রয়েছে। ব্যয় মানে শুধু অর্থনৈতিক নয়, পরিবেশ ও মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের ওপর তার একটি প্রতিকূল প্রভাব আছে। উপরন্তু, ওই অঞ্চলের পানির ওপরও এর বিরূপ প্রভাব রয়েছে। কোন বিদ্যুৎ উৎপাদনে কতখানি পানি লাগে, সেটিও বিবেচ্য। পারমাণবিক শক্তি আর কয়লায় সবচেয়ে বেশি পানি প্রয়োজন হয়। কাজেই পানি কম থাকলে আমরা সেদিকে যেতে পারব না। আবার কয়লা থেকে বাতাস ও স্থানীয় পানির প্রদূষণ সবচেয়ে বেশি। যেখানে পর্যাপ্ত জায়গা নেই, সেখানে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন না করাই ভালো। অন্তত কয়লার ব্যবহার কমিয়ে আনা জরুরি। এসব বিষয় যদি নীতির মধ্যে আসে যে, জ্বালানি সেবা (এনার্জি সার্ভিসেস) চাই, বাংলাদেশে বিদ্যমান জ্বালানি সেবা আরো বাড়াতে হবে, তাহলে কেউ এটা নিয়ে প্রশ্ন করবে না। এটি নিঃসন্দেহে সত্যি। কিন্তু কতখানি বাড়াতে হবে— এটি একটি প্রশ্ন। কীভাবে বাড়াতে হবে— সেটি আরেকটি প্রশ্ন।
আমি বলতে চাইছি, আমরা কী মডেলের উন্নয়ন করব? ভারত ও চীনের উদাহরণ দেয়া যাক। প্রতি হাজার ডলার জিডিপি বাড়াতে চীন ভারতের চেয়ে অনেক বেশি জ্বালানি খরচ করে। কারণ চীনের ম্যানুফ্যাকচারিং (উৎপাদন খাত) সবচেয়ে জ্বালানিনিবিড়; যাকে আমরা ডার্টি ম্যানুফাকচারিং বলি। ওই ম্যানুফ্যাকচারিং বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে চীন নিয়েছে। কাজেই চীনের জ্বালানির বড় অংশ যায় ওই ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে এবং সেটি লো এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং। ভারতের আগে এমন উৎপাদন খাত ছিল। কিন্তু গত ১৫-২০ বছরের ভারতের অর্থনীতির গতি দেখলে দেখা যাবে, ভারতের অর্থনীতিকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে সেবা খাতের বৃদ্ধি। সেবার ক্ষেত্রে এক হাজার ডলার জিডিপি তৈরি করতে গেলে জ্বালানি লাগে উৎপাদন খাতের অর্ধেক। কাজেই আমরা যদি অনেক কম জ্বালানি দিয়ে উচ্চমানের এইচডিআই করতে পারি, তাহলে সেদিকেই আমাদের যাওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, জ্বালানি বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু প্রতি ইউনিট জ্বালানি বাড়াতে একটি পরিবেশগত, শরীর-স্বাস্থ্যের এবং সামাজিক ব্যয় (জমি নেয়া, জঙ্গল কাটা) আছে। সুতরাং একই রকম উন্নয়নের জন্য কম জ্বালানি খরচ করতে পারলে সেটি সবচেয়ে ভালো। এটিকে আমাদের হাইলাইট করতে হবে।
অনেক দেশে কয়লার উপযোগিতা শেষ হলেও বাংলাদেশ কয়লার দিকে ঝুঁকছে। তার বড় উদাহরণ রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র। এটাকে কীভাবে দেখেন?
বিশ্বের অনেক দেশ একটি পর্যায় পর্যন্ত কয়লার ওপর নির্ভর করেছিল। কয়লার উপযোগ বেশি শুরু হয়েছিল ১৮৭০-এর দশকের দিকে। ১৯৭৫ অবধি কয়লা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনটি কারণে কয়লার ব্যবহার কমিয়ে দেয়া হয়। একটা কারণ তো খুব পরিষ্কার। জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি দায়ী কয়লা। দুই. কয়লার বাকি ক্ষতি। কয়লায় প্রদূষণ অনেক বেশি। এক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড শুধু একটি গ্যাস মাত্র, যা জলবায়ু পরিবর্তনের অনুঘটক। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যখন কয়লা জ্বালানো হয়, তখন প্রায় ৫৫-৫৬ ধরনের অন্য প্রদূষণকারী বেরিয়ে আসে; যার মধ্যে অনেক ভারী ধাতু আছে, যেগুলো ক্যান্সার, ব্রেন, জন্মত্রুটিসহ বিভিন্ন কিছুর জন্য দায়ী। তিন. কয়লার ক্ষেত্রে রেগুলেশন শুরু হলে সামগ্রিকভাবে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের দাম বেড়ে যায়। ফলে বিশ্বব্যাপী কয়লার প্রতি অনাগ্রহ দেখা দেয়।
লক্ষণীয়, ভারতসহ কয়েকটি দেশ জেনে-বুঝে নিজেদের কয়লার দাম কম করে রেখেছে। তা না হলে কয়লার দাম এত বেশি হতো যে, কেউ এ থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কিনতে পারত না। বর্তমানে যেখানে সূর্যের আলো বেশি পড়ে, সেখানে সোলার প্লান্ট এবং যেখানে একটু বেশি হাওয়া চলে, সেখানে উইন্ড প্লান্ট তৈরি করা হয়। দুটো ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের দাম কয়লার চেয়ে কম। এনটিপিসির হিসাব হলো, সস্তার কয়লায় নতুন প্লান্টে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়বে ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আর নতুন সোলার প্লান্টে খরচ পড়বে ২ টাকা ৬০ পয়সা থেকে ২ টাকা ৯০ পয়সা। সুতরাং প্রদূষণের বিষয়টি ছেড়ে দিলেও কয়লা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম অনেক বেশি। সেজন্য ভারতে কয়লাভিত্তিক প্লান্ট স্থাপন একদম কমে গেছে। ২৫ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বেচার জন্য ফেলে রাখা হয়েছে, কোনো ক্রেতা নেই।
ভারতের এনটিপিসি ও বাংলাদেশ সরকারকে বলছি, সুন্দরবনের মতো স্পর্শকাতর জায়গায় এত লোকের বিরোধিতা সত্ত্বেও কেন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করছেন? ভারতে বর্তমানে ৩ লাখ ৩৫ বিজলিঘর (বিদ্যুৎকেন্দ্র) প্রস্তুত হয়ে বসে রয়েছে। আর আমাদের সর্বোচ্চ চাহিদা ১ লাখ ৭২ হাজার মেগাওয়াট। বাংলাদেশ ভারত সরকারকে বলুক ৫-১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বিক্রি করতে। কয়লা আমদানি করা হবে, সুদাসলে প্রচুর অর্থ এনটিপিসিকে দেয়া হবে, নির্মাণ হতে তিন-চার বছর লাগবে, তার ওপর সুন্দরবনের ক্ষতি হবে। কাজেই কোনো দিক থেকে রামপাল প্রকল্প লাভজনক নয়। এ অবস্থায় বাংলাদেশকে বরং ভারত বিদ্যুৎ দিক। ভারত যত বিজলিঘর বানিয়েছে, তার বাজার নেই। গত বছর স্পট মার্কেটে ১ টাকা ৮৬ পয়সায় বিদ্যুৎ বিক্রি হয়েছে। মধ্য প্রদেশ সরকার ২ টাকা ৬২ পয়সায় অন্য রাজ্যগুলোকে বিক্রি করেছে। নিজেদের বাকি চারটি বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে রেখেছে।
বাংলাদেশের বিদ্যুতের চাহিদা কত? ১০-২০ হাজার মেগাওয়াট। দিক না ভারত। কেউ আপত্তি করবে না। এতে সুন্দরবনও নষ্ট হবে না। বাংলাদেশ ওই পর্যায় থেকে সোলার, উইন্ড বা গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জ্বালানিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, যার দাম কয়লা থেকে অনেক কম।
পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যাপারে আপনার মত কী?
পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ থেকে বাংলাদেশের একদমই বিরত থাকা উচিত। এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিপদ শুধু দুর্ঘটনায় নয়; এর সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, রেগুলার চলার সময় সেগুলো ভেন্টিং করতে হয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে রেড়িওঅ্যাকটিভ প্রসেসে ইউরিয়াম ভাঙা হয়। এতে সৃষ্টি হয় কিছু উপজাত। তার মধ্যে আছে অনেক তেজস্ক্রিয় গ্যাস। সেগুলোও রেডিওঅ্যাকটিভ এবং অনেক বছর রেডিওঅ্যাকটিভ থাকবে। রিঅ্যাক্টর বিল্ডিংয়ে গ্যাসগুলো জমা হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে চিমনি দিয়ে ভেন্টিং করতে (বা ছেড়ে দিতে) হয়। ওই গ্যাসগুলো ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের বাতাসে। সেগুলোর অনেকটাই নেমে আসে নিচে ৫-১০ কিলোমিটারের মধ্যে। রেডিয়েশন বাইরে কম থাকলে খুব একটা উদ্বেগ নেই, কিন্তু তা নিঃশ্বাসের সঙ্গে মানবদেহের ভেতরে গেলে মানুষের টিস্যু ও ডিএনএর ক্ষতি করতে পারে। ক্যান্সার হতে পারে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্মগত ত্রুটি হতে পারে। সারা বিশ্বে এর অনেক নজির আছে। তার ওপর বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো ফুয়েল চেইন নেই। এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল, হাই-টেকনোলজি প্রসেস এবং খুব ঝুঁকিপূর্ণ। উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী থাকলে আরো বেশি ঝুঁকি। ইউরেনিয়ামের অবশিষ্টাংশ নিয়ে তৈরিকৃত ডার্টি বোমা কেমিক্যাল বোমার সঙ্গে ফাটিয়ে দিলে কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে রেডিওঅ্যাকটিভ ম্যাটারিয়েল ছড়িয়ে পড়বে। এটা খুব বিপজ্জনক বিষয়।
তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, রাশিয়া রিঅ্যাক্টর দেবে আর ভারতের নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনপিসিআইএল) সেটা সামলাবে। কিন্তু তার ব্যয় কত হবে? এবার আর্থিক হিসাবে আসুন। ভারতে বর্তমানে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম ইউনিটপ্রতি ৮-৯ টাকার কম না। এর মধ্যে সরকার কিছু ভর্তুকি দেয়, যা হিডেন (লুক্কায়িত)। তবু ৫-৬ টাকার নিচে না। বর্তমানে একটি স্ট্যান্ডার্ড জায়গা যেমন— মধ্যপ্রদেশে ২ টাকা ৯০ পয়সায় সৌরবিদ্যুৎ পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যদি ২ টাকা ৯০ পয়সা থেকে ৩ টাকায় বাতাস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, বাংলাদেশেও পাওয়া যাবে। বাংলাদেশ তো এসব অঞ্চল থেকে একদম আলাদা নয়। ভারতীয় ৩ টাকায় এখানেও বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। কাজেই বাংলাদেশ সরকার এত ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে কেন যাবে, যার ওপর নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। সোলার বা উইন্ড বিদ্যুৎকেন্দ্র করলে পুরো নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের থাকবে, অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।
সেভাবে গবেষণা না হলেও অনেকেই বলছেন, বাংলাদেশে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সোলার ও উইন্ডের সম্ভাবনা কম। আপনার কী মত?
বাংলাদেশের জন্য বিকল্প কম— এটা তারাই বলেন, যারা জানেন না। একটি এক মেগাওয়াটের সোলার বিজলিঘরের জন্য সব মিলিয়ে পাঁচ একরের মতো জায়গা লাগে। মনে করুন, একটি গ্রাম আছে, যেখানে তিনশ-পাঁচশ বাড়ি। পাঁচশ ঘরের জন্য ৫০০ কিলোওয়াটের প্লান্ট যথেষ্ট। এজন্য এক একর জমি লাগবে। একটি গ্রাম এক একর জমি দিতে পারবে না? আবার শহরাঞ্চলের ফ্যাক্টরি, স্কুল, হাসপাতাল, নার্সিং হোম, পার্কিং জায়গা, বাসাসহ সব ছাদ ব্যবহার করা হলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদার একটি বড় অংশ স্রেফ রুফটপ থেকে আসতে পারে। যারা একেবারে অজ্ঞ, তারা বলেন যে, সোলারে হবে না। কেন হবে না, সেটা বোঝাতে পারেন না।
উইন্ডের বিষয়ে আমি আবারো বলব, ৮০ মিটার হাব হাইটের উইন্ড এরিয়াগুলো সার্ভে করা হোক, সম্ভাবনা (পটেনশিয়াল) অনেক বেড়ে যাবে। তাছাড়া বাংলাদেশের একটি বড় উপকূলীয় এলাকা আছে, যেখানে দুই রকম এনার্জির সম্ভাবনা রয়েছে। এক. সুনির্দিষ্ট কিছু এলাকায় টাইডাল এনার্জি পাওয়া যেতে পারে। টাইডাল এনার্জির প্রভাব বেশি। এক্ষেত্রে ড্যাম না হলেও ছোট অবস্ট্রাকশন দিতে হয়। দুই. কিছু এলাকায় ওয়েভ (তরঙ্গ) এনার্জি পাওয়া যেতে পারে। এটি একটি সাবস্টেনশাল এনার্জি। আমরা হাওয়া থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারলে তরঙ্গ থেকেও পারব। কারণ হাওয়ার চেয়ে পানির ঘনত্ব ৮০০ গুণ। ওয়েভ এনার্জির কিছু মডেল ডেমোনস্ট্রেশন শুরু হয়েছে, কিছু কিছু বাণিজ্যিকীকরণও হয়েছে। এটি হয়তো আরেকটু সময় লাগবে। আমরা তো পাঁচ বছর বা স্বল্প সময়ে পুরো জ্বালানি ব্যবস্থা বদলানোর কথা বলছি না। আগামী ২০-২৫ বছরে বাংলাদেশ যেন অনেক বেশি ক্লিন এনার্জির ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে পারে, আমরা তার কথা বলছি। তার মধ্যে ওয়েভ, সোলার, উইন্ড সবই রয়েছে। বর্তমানে সোলার, উইন্ডে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এসেছে। টাইডাল বা ওয়েভ এনার্জির প্রযুক্তি সর্বাধুনিক (ম্যাচিউর) হতে আগামী পাঁচ বছর সময় লাগবে। কিন্তু একটি দেশের জন্য ১০, ১৫, ২০ বছরের পরিকল্পনা তো থাকে। বাংলাদেশ ২০৪১ অবধি পরিকল্পনা করছে। এর মধ্যে সব প্রযুক্তি সর্বাধুনিক হবে।
আরেকটি ফ্যাক্টর আমাদের মাথায় রাখতে হবে, কয়লার রেগুলেশন বাড়ছে, বাড়বে। লোকে বলবে, কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হলে প্রদূষণ কম করতে হবে। সেক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার প্রয়োজন হবে। তাতে খরচ বাড়বে। কাজেই যারা বলেন, সোলার ও উইন্ড দিয়ে হবে না; আমি বলব, তারা হিসাবের পাটিগণিতই বোঝেন না। (বণিক বার্তা)
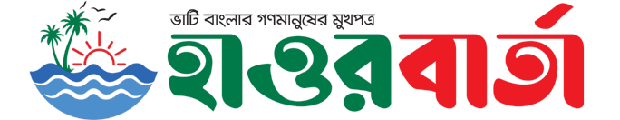
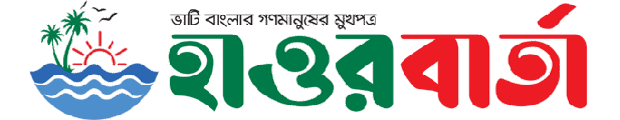
 Reporter Name
Reporter Name 
























