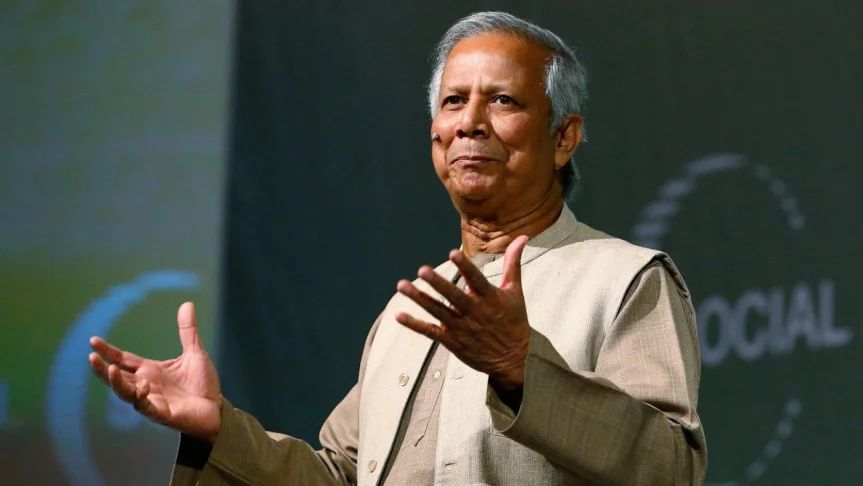হাওর বার্তা ডেস্কঃ বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীরা খাদ্যের অভাবে প্রাণ হারাতে পারে বলে সেভ দ্য চিলড্রেনের দেওয়া সতর্কবাণী আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। একই সঙ্গে আমাদের জন্য এটা উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে শরণার্থী হয়ে আসা শিশুদের ৮৫ ভাগই রোগাক্রান্ত। এই সতর্কবাণী ও শিশুদের অবস্থা আমাদের ১৯৭৮-৭৯ সালের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই সময় দুই লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের যে অভিজ্ঞতা, তাকে মর্মান্তিক বললে কম বলা হবে।
সেই সময়ের ঘটনার বিস্তারিত আলোচনার আগে আমাদের এখনকার পরিস্থিতি স্মরণ করা দরকার। ইতিমধ্যে চার লাখের বেশি শরণার্থী জীবন রক্ষার জন্য পালিয়ে এসেছে, তাদের সংখ্যা বাড়তে পারে এবং এই সংখ্যা ১০ লাখে গিয়ে দাঁড়ানোর আশঙ্কার কথাও বলেছেন আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা। ইতিমধ্যেই এই শরণার্থী সমস্যাকে ‘সবচেয়ে স্বল্প সময়ে সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয়গুলোর অন্যতম’ বলে বর্ণনা করেছে জাতিসংঘ। ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডার জাতিগত সংঘাতের সময় পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নেওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল ২ লাখ, ২০১৬ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলো থেকে ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইউরোপে শরণার্থী হতে চেষ্টা করেছে, এমন মানুষের সংখ্যার চেয়েও এই সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি। তাতেই স্পষ্ট যে এই সংকট আগের যেকোনো শরণার্থী-সংকটের চেয়ে অনেক বড় আকারের।
বাংলাদেশ সরকার গোড়াতে এই রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে যে একধরনের দোদুল্যমানতায় ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। যে কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়ার আহ্বানকে ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ (ইরেসপনসিবল) বলে সমালোচনা করেছিলেন (হাওর বার্তা, ‘রোহিঙ্গা বিষয়ে খালেদা জিয়ার মন্তব্য “ইরেসপনসিবল”’, ২৯ আগস্ট ২০১৭)। তদুপরি বাংলাদেশ মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্তে যৌথ নিরাপত্তা অভিযানের প্রস্তাব করেছিল। ২০১২ সালে বাংলাদেশ যদিও বাধ্য হয়ে প্রায় ৭০ হাজার শরণার্থীকে জায়গা দিয়েছিল, কিন্তু নীতিগতভাবে সরকারের অবস্থান ছিল রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার। অতীতে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গার ব্যাপারে মিয়ানমার ও আন্তর্জাতিক সমাজের নীরবতাই এর অন্যতম কারণ বলে বোঝা যায়। সৌভাগ্যজনকভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যেই সরকার এই অবস্থান থেকে সরে এসে এই বিপর্যয়কে মানবিকভাবে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শরণার্থী শিবিরে উপস্থিত হয়ে ও জাতীয় সংসদে বলেছেন, ‘১৬ কোটি মানুষের খাবার দিই৷ সেই সঙ্গে কয়েক লাখ মানুষকে খাবার দেওয়ার সক্ষমতা বাংলাদেশের আছে।’ (হাওর বার্তা, ‘রোহিঙ্গা-সংকটের সৃষ্টি মিয়ানমারের, সমাধানও তাদের হাতে’, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭)।
বাংলাদেশ এই লাখ লাখ শরণার্থীর দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, যখন দেশটি এই শরণার্থী-সংকটকে কেন্দ্র করে একাদিক্রমে মানবিক, কূটনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। এই শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত মানবিক বিবেচনাপ্রসূত এবং নিঃসন্দেহে লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত। এটি সারা বিশ্বের প্রশংসা লাভ করেছে। ১৯৭৮ সালেও বাংলাদেশকে এই ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।
১৯৭৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী যখন আরাকানে অভিযান শুরু করে, তখনই সেখান থেকে হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে শুরু করে। বাংলাদেশ রেঙ্গুন সরকারকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় ‘মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি’ নেওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারি ও মার্চে শরণার্থীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পরিস্থিতির বড় রকমের অবনতি ঘটে এপ্রিলে। এপ্রিলের শুরুতে রাষ্ট্রপতি জিয়ার উপদেষ্টা কাজী আনোয়ারুল হক রেঙ্গুন সফর করে বাংলাদেশের উদ্বেগের কথা জানান এবং রেঙ্গুন আশ্বস্ত করে যে তারা এই বিষয়টি দেখছে। ১৩ এপ্রিল বার্মার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা সফর করেন। তারপরই বাংলাদেশ জানতে পারে যে সীমান্তে বর্মি সৈন্য সমাবেশ বাড়ানো হয়েছে; পলায়নপর শরণার্থীদের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে এবং ২৩ তারিখ থেকে বার্মার সৈন্যদের সঙ্গে বিডিআরের কয়েক দফা পাল্টাপাল্টি গুলির ঘটনা ঘটে। ২৭ এপ্রিল বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রসচিব মঞ্জুর আহমেদ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করে জানান যে প্রায় ২০ হাজার শরণার্থী ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে এবং বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয়ভাবে তা সমাধানের চেষ্টা করছে (যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কেবল, ২৭ এপ্রিল ১৯৭৮, ১৯৭৮ ঢাকা ০২৬৩৯ _ডি)।
কিন্তু সেই প্রচেষ্টায় সাফল্যের বদলে পরের কয়েক সপ্তাহে শরণার্থীর সংখ্যা বেড়ে লাখের কোটায় গিয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিকভাবে সরকার ১২টি এবং পরে আরও একটি শিবির স্থাপন করে। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় শরণার্থীদের নিবন্ধন ও ত্রাণ বিতরণের। মে মাসে শরণার্থীর সংখ্যা দেড় লাখে পৌঁছালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। জাতিসংঘের মহাসচিব এই দায়িত্ব দেন ইউএনএইচসিআরের ওপর; কিন্তু বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআরের কোনো অফিস না থাকায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) প্রধান বার্নার্ড জাগোরিনকে এই দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করে কেন্দ্রীয় দপ্তর এবং পরে ইউএনএইচসিআরের একজন কর্মকর্তা রোমান কোয়াহুটকে ঢাকায় পাঠানো হয় তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে মোট সাড়ে ১৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের আবেদন জানানো হলে ১২টি দেশ এবং বিভিন্ন সংস্থা থেকে মোট ১৪ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার ইউএনএইচসিআরের হাতে পৌঁছায়, আর দ্বিপক্ষীয়ভাবে ১২ দশমিক ৭ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশের হাতে এসে পৌঁছায় বলে ইউএনএইচসিআরকে জানানো হয়।
কিন্তু তারপর কী ঘটেছিল সেটি ১৯৭৯ সালে বিস্তারিতভাবে একটি রিপোর্টে তুলে ধরেছেন সেই সময়ে কক্সবাজারের ইউএনএইচসিআরের সাব অফিসের প্রধান অ্যালান সি লিন্ডকুইস্ট। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে তিনি এই রিপোর্ট তৈরি করেন। তিনি লিখেছেন, ‘এত সব সাহায্য সত্ত্বেও জুলাই মাসে এটা স্পষ্ট হতে থাকল যে ত্রাণ তৎপরতায় সবকিছু ভালোভাবে চলছে না। সরকারি হিসাব অনুযায়ী জুন মাসের গোড়ার দিকে শিবিরগুলোতে মৃত্যুর হার হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে প্রতি ১০ হাজারে ৭ জন, অর্থাৎ বছরে ৪ শতাংশ।’ বাংলাদেশের গড় মৃত্যুর হার থেকে এটা ছিল দ্বিগুণ। ‘জুলাই মাসের শেষে সেই হার গিয়ে দাঁড়াল প্রতি সপ্তাহে প্রতি ১০ হাজারে ১৭ জন, বার্ষিক হিসাবে তা দাঁড়ায় ৯ শতাংশে।’ লিন্ডকুইস্টের সেই রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে চার মাস পর, ২৬ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর, তা গিয়ে দাঁড়ায় বার্ষিক ১৭ শতাংশে—প্রতি সপ্তাহে প্রতি ১০ হাজারে ৩৩ জন। গড়ে প্রতিদিন ৮০ থেকে ৮৫ জন শরণার্থী মারা যাচ্ছিল, যার ৭০ শতাংশই ছিল শিশু। ছয় মাসে মারা গিয়েছিল প্রায় সাড়ে সাত হাজার মানুষ, ১৯৭৯ সালে জানুয়ারি মাসে ইউএনএইচসিআরের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে ১০ হাজার মানুষ। মার্চে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১২ হাজারে।
অ্যালান সি লিন্ডকুইস্ট খুব কাছে থেকে এই সব মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন। এর কারণগুলোও তাঁর রিপোর্টে বিস্তারিতভাবেই বলা আছে। যদিও জাতিসংঘের সম্মতি নিয়েই বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক শরণার্থীর জন্য প্রতি সপ্তাহে ১৯১০ ক্যালরি, শিশুদের জন্য এর অর্ধেক ক্যালরিসম্পন্ন খাবারের রেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল; যদিও ৭০০ টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল, যদিও বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি প্রতিটি শিবিরে চিকিৎসা ক্লিনিক স্থাপন করেছিল, যদিও ‘ভালনারেবল’ বলে চিহ্নিতদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তথাপি শেষ পর্যন্ত এই বিশালসংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে সবকিছু কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল এবং কার্যত এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল যে শরণার্থীদের জন্য এমন ব্যবস্থা করা, যাতে তারা বাংলাদেশে থেকে যাওয়ার চেয়ে বার্মায় ফিরে যেতে উৎসাহী হয়।
এই নিয়ে ঢাকায় কর্মরত খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) পুষ্টিবিদ ডক্টর কাটো আল, যিনি ইউএনএইচসিআরের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, বারবার অনুরোধ করেও বোঝাতে পারেননি যে পুষ্টিহীনতাই এসব মৃত্যুর কারণ। লিন্ডকুইস্টের রিপোর্টের কারণে আমরা এই জানি যে কাগজপত্রেও রিলিফের খাবার কম বিতরণের হিসাব ছিল এবং তিনি ‘দুর্নীতি’র কথাও বলেছেন। এই পরিস্থিতির জন্য সরকারি নীতি যে কতটা দায়ী, সেটা বোঝাতে তিনি ঢাকার সরকারি দপ্তরে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব বলেছিলেন, ‘ভদ্রমহোদয়গণ, এটা খুব ভালো ব্যাপার, যদি শরণার্থীরা ভালোভাবে খেয়ে থাকে। কিন্তু আমাকে রাজনীতিবিদের মতো বলতে হবে, আমার শরণার্থীদের এমন আরামে রাখব না যে তারা যেন বার্মায় ফিরে না যায়।’
এই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছিল ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএআইডির কর্মকর্তারা ৭ থেকে ৯ ডিসেম্বর শরণার্থী শিবিরগুলো ঘুরে এসে ওয়াশিংটনে প্রতিবেদন পাঠান এবং তা জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসেও পাঠানো হয়, যাতে তারা বিষয়টি ইউএনএইচসিআরের সদর দপ্তরে তোলে। ইউএসএআইডির এই গোপন প্রতিবেদন ফাঁস হয়ে যায়, তার ভিত্তিতে লন্ডনের অবজারভার-এ ১৯৭৯ সালের ২১ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় দীর্ঘ প্রতিবেদন।
১৯৭৮ সালের জুলাই মাসেই এই শরণার্থীদের ব্যাপারে বার্মার সঙ্গে চুক্তি সই হয়েছিল এবং তারা শেষ পর্যন্ত স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল। কূটনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে এটি নিশ্চয় এক বড় সাফল্য কিন্তু মানবিক বিপর্যয়ের একটি উদাহরণ বলেও একে মনে রাখতে হবে। এই ঘটনা থেকে বাংলাদেশ সরকার ও ত্রাণ তৎপরতায় যুক্তরা কতটা শিক্ষা গ্রহণ করেছে, সেটা আমাদের জানা নেই, কিন্তু এটা আমরা জানি যে এবার এর চেয়েও বড় ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয়, যারা পালিয়ে এসেছে, তাদের অধিকাংশ হচ্ছে নারী ও শিশু। তাদের আরও বিভিন্ন ধরনের বিপদের লক্ষণ ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সরকার এসব বিষয়ে দ্রুত ও যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে না পারলে এক বিপর্যয় থেকে পালিয়ে এসে শরণার্থীরা অনাহারে ও অবহেলায় মৃত্যুবরণ করবে। আমরা মানবিক হওয়ার যে কথা এখন বলছি, তখন তা বলা সম্ভব হবে না।


 Reporter Name
Reporter Name