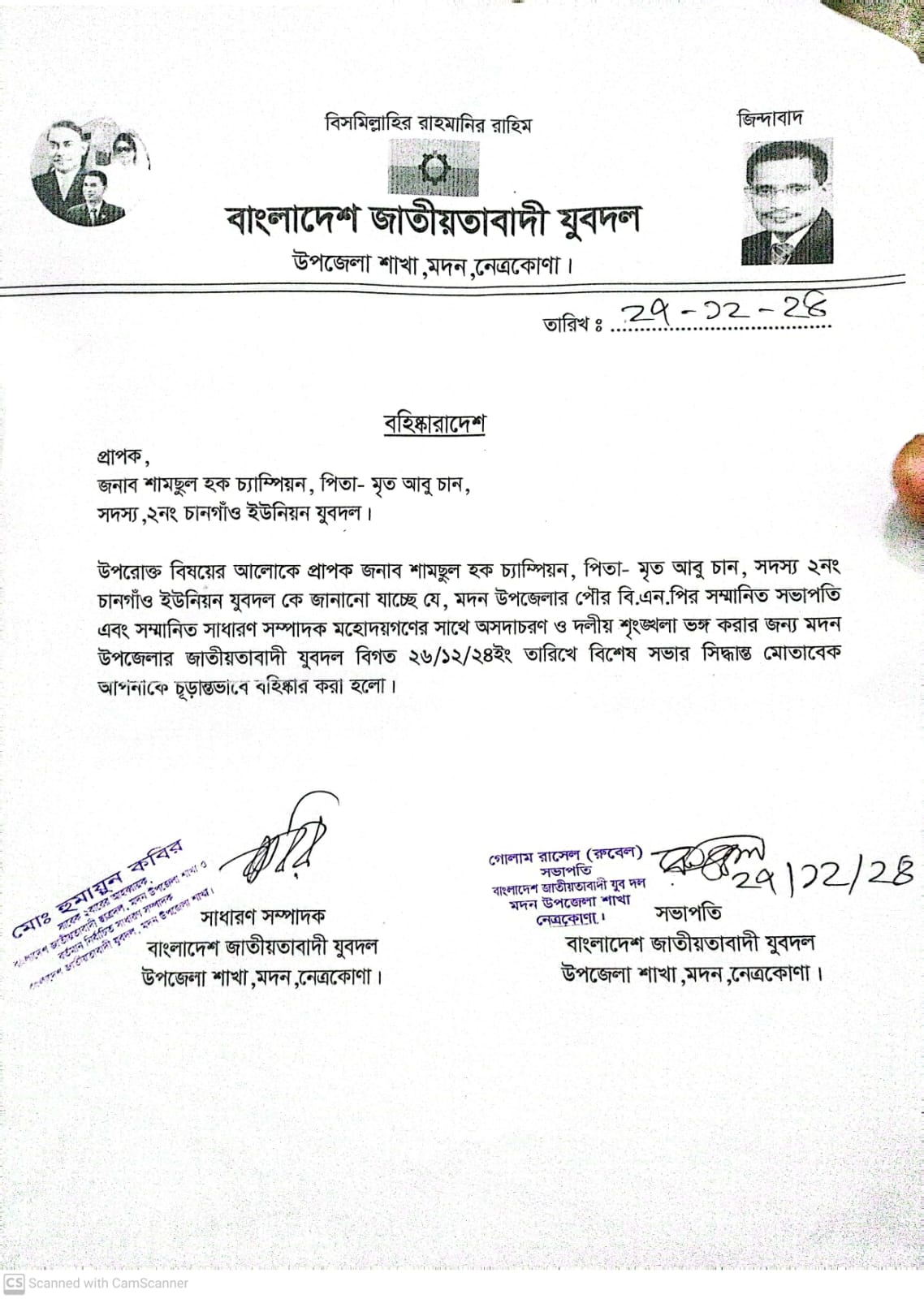হাওর বার্তা ডেস্কঃ কিশোরগঞ্জ শহরের ঐতিহাসিক স্থাপনার মধ্যে পাগলা মসজিদ অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। শহরের পশ্চিমাংশে নরসুন্দা নদীর তীরে মাত্র ১০ শতাংশ ভূমির উপর এই মসজিদটি গড়ে উঠেছিল। সময়ের বিবর্তনে আজ এ মসজিদের পরিধি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে এর খ্যাতি ও ঐতিহাসিক মূল্যও। মূল মসজিদ পূর্বের তুলনায় অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। এর পাশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি মাদ্রাসা। দিনে দিনে মসজিদের শ্রীবৃদ্ধিই শুধু ঘটছে না, ঘটছে এর উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ। মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি অত্যাধুনিক ধর্মীয় কমপ্লেক্স এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
পাগলা মসজিদের নির্মাণকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ঈশা খাঁ’র ৫ম পুরুষ দেওয়ান হৈবৎ খাঁ বর্তমান হয়বতনগর এলাকায় তার জমিদারি প্রতিষ্ঠা করে বসতবাটি স্থাপনের পর এ এলাকাটি হয়বতনগর নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৬৭৩ খ্রি. থেকে পরবর্তী একশত বছর আজকের কিশোরগঞ্জ অঞ্চলটি হয়বতনগর নামেই পরিচিত ছিল। সময় যেতে যেতে সেই পরিচয়ের বলয় সংকুচিত হয়ে হয়বতনগর আজ নিছক একটি গ্রাম বা মহল্লার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।
হয়বতনগর জমিদারবাড়ির বর্তমান প্রতিনিধি সৈয়দ রেজওয়ান উল্লাহ বাসারের কাছে রক্ষিত পারিবারিক ঠিকুজি পর্যালোচনা করে অনুমিত হয় যে, দেওয়ান হৈবৎ খাঁ’র ধারাবাহিকতায় ঈশা খাঁ’র ৭ম পুরুষ দেওয়ান জিলকদর খান সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হয়বতনগরের জমিদার হয়েছিলেন। বংশ-তালিকার ধারাক্রমে জিলকদর খান দেওয়ান হৈবৎ খাঁ’র পৌত্র বা দৌহিত্র ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। জমিদারি প্রাপ্ত হলেও দেওয়ান জিলকদর খানের জমিদারির প্রতি কোনোরূপ মোহ ছিল না। তিনি জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাইরে অনেকটা আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী থাকতেন। সংসার-বিবাগী ও উদাসী প্রকৃতির এই মানুষটি সবার কাছে ‘পাগলা সাহেব’ নামে পরিচিত ছিলেন। জমিদারির নৈমিত্তিক দায়িত্বের প্রতি তার কোনো মনোযোগ ছিল না। প্রায়শই তিনি আজকের পাগলা মসজিদ যেখানে স্থাপিত, সেখানে এসে ধ্যানমগ্ন ঋষীর মতো বসে থাকতেন। নরসুন্দাপাড়ের এই স্থানটিকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন তার প্রাত্যহিক ধ্যানের স্থান হিসেবে। পরে জমিদারবাড়ির তত্ত্বাবধানে পাগলা সাহেবের আরাধনার জন্য এই স্থানটিতে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ তৈরি করে দেওয়া হয়। এ কারণেই পরবর্তী সময়ে মসজিদটির নাম পাগলা মসজিদ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। ১৮৮৫ সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে শতাব্দীর ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এতে হয়বতনগর জমিদারবাড়িসহ অনেক স্থাপনা ধ্বংস হয়ে যায়। বিলুপ্ত হয়ে যায় ক্ষুদ্রকায় পাগলা মসজিদটিও। পরে জমিদারবাড়ির অর্থায়নে নতুন করে জমিদারবাড়িটি যেমন গড়ে ওঠে, তেমনি পাগলা মসজিদকেও নতুনভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জমিদারবাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখা হয়।
সি.এস রেকর্ডে ৩৩০৩ ও ৩৩৮২ খতিয়ানটি হয়বতনগরের তৎকালীন ১২ আনা অংশের জমিদার আয়েশা আক্তার খাতুন ও চারআনা অংশের জমিদার সৈয়দ রাজিউল্লাহ গংয়ের নামে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সিএস ২৩৯৪ নম্বর দাগের ১০ শতাংশ ভূমিতেই স্থাপিত হয় পাগলা মসজিদ। রেকর্ডে দখলকার হিসেবে মসজিদের খাদেম তালেব আলী মুন্সির নাম পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন এ মসজিদটি খাদেমের নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হয়।
মসজিদকে নিয়ে জনশ্রুতি:
মসজিদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশকিছু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। একটি জনশ্রুতিএ-রকম, একবার নরসুন্দার প্রবল জলস্রোতে মাদুর পেতে এক আধ্যাত্মিক পুরুষ ভেসে আসেন। তার আসন ছিল নদীর ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে। বর্তমান মসজিদের কাছে এসে সে আধ্যাত্মিক পুরুষ স্থিত হন। এভাবেই কয়েকদিন কেটে যায়। তারপর ধীরে ধীরে নদীর সে স্থানটিতে জেগে ওঠে চরাভূমি। সাধক তখনও ধ্যানমগ্ন। জেলেরা মাছ ধরতে এসে এ অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পায়। সবাই বিস্মিত এবং হতবাক। কেউ কাছে এগিয়ে আসার সাহস করে না। এরই মধ্যে নদীর বিপরীত দিকে অবস্থিত রাখুয়াইল গ্রামের এক গোয়ালা হঠাৎ লক্ষ করল, তার পালিত সদ্য প্রসবিনী গাভীর ওলানে কোনো দুধ আসছে না। অনেক চেষ্টা করেও সে একফোঁটা দুধও পেল না। এরই মধ্যে একদিন গাভীটি পাল থেকে বেরিয়ে নদী সাঁতরিয়ে সেই আধ্যাত্মিক সাধকের চরায় উঠে আসে। সাধকের পাশে রক্ষিত একটি পাত্রে ওলানের সম্পূর্ণ দুধ ঢেলে দিয়ে গাভীটি আবার নদী সাঁতরিয়ে ফিরে আসে পালে। এ-রকম পরপর কয়েকদিন ঘটলো। সব দেখে গোয়ালা নিশ্চিত হলো যে, এ সাধক এক কামেল পুরুষ । তাই গোয়ালা সেই সাধক পুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। কিছুদিনের মধ্যেই গোয়ালার সংসারে অভাবনীয় উন্নতি হতে থাকে। গোয়ালার উন্নতি দেখে আশেপাশের জেলে-তাঁতী থেকে শুরু করে অনেকেই সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পরে শিষ্যদের মাধ্যমেই এ স্থানে গড়ে ওঠে একটি হোজরাখানা। সাধকের মৃত্যুর পর হোজরার পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে হোজরাখানার পাশেই নির্মিত হয় একটি মসজিদ; যা পরে পাগলা সাধকের নামানুসারে পাগলা মসজিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।
গুরুদয়াল কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক জিয়াউদ্দীন আহমদ পাগলা মসজিদ নিয়ে দৈনিক বাংলায় একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেই নিবন্ধে তিনি দাবি করেন, হৈবৎ খানের অধস্থন পুরুষ জোলকরন খানের স্ত্রী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই মসজিদটি স্থাপন করেন। জমিদার-জায়া আধ্যাত্ম সাধনায় ব্রতী থাকতেন এবং নিঃসন্তান ছিলেন। জনসাধারণের কাছে পাগলাবিবি নামে তিনি পরিচিত ছিলেন বলে তার প্রতিষ্ঠিত মসজিদটির নাম হয় পাগলা মসজিদ। অবশ্য মসজিদ এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান ও সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তিত ধারা বিশ্লেষণ করে এমন মতবাদও তৈরি হয়েছে যে, এ এলাকায় একসময় বৌদ্ধ, যোগী ও নাথযোগী সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। বিগত শতকে এখান থেকে ‘হাড়মালা’ ‘মধ্যযুগ’ ‘যুগমালা’ ও ‘যুগধর্ম রহস্য’ নামের হস্তলিখিত বেশকিছু পাণ্ডুলিপিও উদ্ধার করা হয়; যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, নরসুন্দা নদীতে জেগে ওঠা চরাভূমিতে একসময় নাথযোগী সম্প্রদায়ের কোনো সিদ্ধ পুরুষ তার সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সিদ্ধপুরুষের শিষ্য বা অনুসারী ছিল স্থানীয় গোয়ালা, জেলে, তাঁতী, মাঝি ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকজন; যারা গোরক্ষনাথের অনুসারী হিসেবে এখানে নানারকম লোকাচার পালন করতো।
পাগলা মসজিদ প্রতিষ্ঠা নিয়ে নানারকম ধারণা ও জনশ্রুতি থাকলেও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ মসজিদ প্রতিষ্ঠার পেছনে হয়বতনগর জমিদারবাড়ির বদান্যতাই সমধিক স্বীকৃত এবং গ্রহণযোগ্য। অথচ দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, যার কারণে এ মসজিদটি গড়ে উঠেছিল সেই আধ্যাত্মিক পুরুষ জমিদার জিলকদর খানের কবরটি আজ হয়বতনগর মাদ্রাসা সংলগ্ন গোরস্তানে অনাদর-অবহেলায় অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। এই মহান পুরুষের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্য তার কবরটি চিহ্নিত করে সংরক্ষণ করা ইতিহাসের প্রয়োজনেই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ।
মসজিদকে ঘিরে লোকবিশ্বাস:
ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে সবার মধ্যেই পাগলা মসজিদকে ঘিরে অনেক লোকবিশ্বাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। মসজিদ প্রতিষ্ঠালগ্নে গৃহস্থরা তাদের গৃহপালিত গাভীর বাচ্চা প্রসবের ২৯ দিনের মাথায় গাভীর প্রথম দুধ দিয়ে নাড়ু বা ক্ষির তৈরি করে এ মসজিদে দিয়ে যেত; যা তাদের ধারণায় গোরক্ষনাথের শিরনি বলে অভিহিত ছিল। এতে গাভী আরও দুগ্ধবতী হবে বলে তারা মনে করতো।
বর্তমান মসজিদ যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে এককালে একটি চৌচালা টিনের ঘর ছিল বলে শতবর্ষী ব্যক্তিদের কেউ কেউ বলে থাকেন। এই টিনের ঘরটিই নাকি মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই ঘরের পশ্চিম-উত্তরপাশে পাথরের টুকরাকৃতির তিন-চারটি ইট ছিল; আর ঘরটির সামনে একটি উঁচু টিলার উপর ছিল একটি চার-পাঁচ হাত দীর্ঘ পাথর। আনুমানিক চারহাত প্রশস্ত এই চৌকা পাথরটির মাঝের অংশ ছিল খাঁজকাটা। এই ইট ও পাথরকে কেন্দ্র করে অনেক লোকবিশ্বাস প্রচলিত ছিল। কুমারী মেয়েরা বর কামনায় এবং বিবাহিত নারীরা সন্তান কামনায় নানা উপাচারসহ পাথরের খাঁজকে সিঁদুরে রঞ্জিত করতো। কেউ কেউ মামলা-মোকদ্দমায় সুবিধা পাওয়ার আশায় কিংবা কারও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ইট উল্টে রাখতো। ইট উল্টে রাখার এই রেওয়াজকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ‘হান উল্ডানি’। পাথরের খাঁজে দুধ ঢেলে মানত করাও ছিল একটি বিশেষ লোকবিশ্বাস। এসব লোকবিশ্বাস ধর্মীয় বিধানে অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় সময়ের বিবর্তনে প্রচলিত লোকাচার এখন আর তেমন দেখা যায় না। তবে পাগলা মসজিদকে নিয়ে মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভিত্ আজও অটুট রয়েছে। ফলে আজও এ মসজিদে মানুষ নানা উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করে থাকেন। দীর্ঘ বছরব্যাপী খাদেমের তত্ত্বাবধানে মসজিদটি পরিচালিত হতো বলে দান-খয়রাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থের কোনো সুনির্দিষ্ট হিসাব রক্ষিত হয়নি; এমনকি মসজিদ উন্নয়নেও তেমন কোনো কাজের নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।
প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ:
গত শতকের পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাগলা মসজিদটি ওয়াকফ প্রশাসনের আওতায় নিবন্ধিত হয়। এ সময় মোতওয়াল্লীর দায়িত্ব পান হয়বতনগর জমিদারবাড়ির দেওয়ান ছাত্তারদাদ খান ওরফে সায়রা মিয়া। মসজিদ কমিটিতে জমিদারবাড়ির চারআনা অংশের জমিদার সৈয়দ মো. রফিকউল্লাহও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ১৯৭৯ সালে মসজিদটির নিয়ন্ত্রণ কিশোরগঞ্জ মহকুমা প্রশাসন গ্রহণ করে। তখন থেকেই মহকুমা প্রশাসক পদাধিকার বলে মসজিদ কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৪ সালে জেলা সৃষ্টির পর থেকে জেলা প্রশাসক মসজিদ কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আসার পর থেকে মসজিদ প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত হয়বতনগর জমিদারবাড়ির কাউকে আর কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হচ্ছে না। এ বিষয়ে সৈয়দ রেজওয়ান উল্লাহ বাসার দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, জমিদারবাড়ি থেকে মসজিদ কমিটিতে একজন প্রতিনিধি রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মহল ঔদার্য দেখালে কোনো ক্ষতি কারণ নেই। এ বিষয়ে তিনি প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উদার দৃষ্টিভঙ্গি কামনা করেন। প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আসার পর থেকে এ মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। পূণ্যার্থীরা সুনির্দিষ্ট দানবাক্সে তাদের দানের অর্থ প্রদান করছেন। প্রতি তিনমাস অন্তর জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দানবাক্স উন্মুক্ত করা হয়। এতে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা এমনকি কখনও কখনও কোটি টাকা প্রতি তিনমাসে অর্জিত হচ্ছে। অর্জিত অর্থ সভাপতি/সম্পাদকের যৌথনামে একটি ব্যাংক একাউন্টে রক্ষিত হয়। বাংলাদেশে আর কোনো মসজিদে এত বিপুল অর্থের দান পাওয়ার নজির নেই। মসজিদ উন্নয়নে নানামুখী কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়ত পরিচালিত হচ্ছে। শহরের একটি দৃষ্টিনন্দন ধর্মীয় স্থাপনা হিসেবে পাগলা মসজিদ আজ সকলের কাছে একটি প্রিয় প্রতিষ্ঠান। মসজিদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হয়েছে। দিন যত যাচ্ছে পাগলা মসজিদের খ্যাতি ও জৌলুস ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলার একটি ঐতিহাসিক মসজিদ হিসেবে পাগলা মসজিদকে নিয়ে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই গৌরব বোধ করেন। এ মসজিদ কিশোরগঞ্জের গর্ব এবং অহংকারের ভিত্কেও উচ্চমার্গে তুলে ধরেছে।
ই বি ডি নিউজ


 Reporter Name
Reporter Name