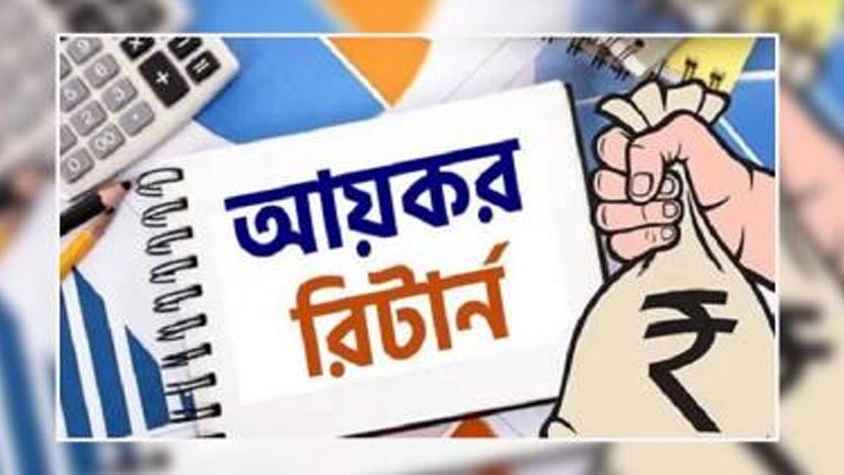আয়তনের দিক থেকে আমাদের দেশটা ছোট হলেও বৈচিত্র্য আর বিশেষত্বের দিক থেকে ছোট নয়। একেক জেলায় একেক ধরনের বিশেষত্ব রয়েছে। এসব বিশেষত্বের আবার রয়েছে রকমফের। খাবার দাবারের কথাই যদি বলি তাহলে আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে বিখ্যাত কিছু স্থানের নাম। যেমন চমচমের জন্য টাঙ্গাইল, দইয়ের জন্য গৌরনদী, রসমালাইয়ের জন্য কুমিল্লা। একইভাবে সমুদ্র সৈকতের জন্য কক্সবাজার ও কুয়াকাটা, বন পাহাড়ের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট, সুন্দরবনের জন্য খুলনা। তবে এসব ছাড়াও আরো কিছু প্রাকৃতিক বিশেষত্ব আছে যার বিকল্প খুব একটা পাওয়া যায় না। চা বা কমলার কথা বললেই চলে আসে সিলেট-মৌলভীবাজারের প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের একমাত্র বুনো ম্যাগনোলিয়া ডুলিচাঁপা সিলেট বা চট্টগ্রামের পাহাড় ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না, কাইজেলিয়ার দুটো পুরনো গাছ শুধুমাত্র রংপুর কারমাইকেল কলেজেই আছে, কেয়া বন আর সুলতানচাঁপা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় উপকূলীয় কয়েকটি জেলায়। প্রকৃতির এমন কয়েকটি বিশেষ উপহার নিয়েই এই আয়োজন।
মৌলভীবাজার (চা, কমলা, দুলিচাঁপা)
চা
চা মানে সিলেট, আর সিলেট মানে চায়ের দেশ। এটা খুব জানা কথা। কিন্তু প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কারণে বেশিরভাগ চা-বাগান পড়েছে মৌলভীবাজার জেলায়। আর শ্রীমঙ্গল হচ্ছে চা-বাগানের প্রাণকেন্দ্র। চায়ের অর্থকরী দিকটা ছাড়াও চা-বাগানের যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য তা সত্যিই উপেক্ষা করা কঠিন। এ কারণে অনেকেই বেড়াতে যান চা-বাগানে। সেখানকার নিঝুম প্রকৃতি ও পাহাড়ের ঢালুতে রীতিবদ্ধ নান্দনিক চা-গাছের বিন্যাস প্রতিনিয়তই মুগ্ধ করে আমাদের। চা- বাগানের ছায়া-বৃক্ষ হিসেবে যে কড়ই গাছগুলো ব্যবহার করা হয় তার সৌন্দর্যও কম নয়। এসব বাগানের কোনো কোনোটিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ক্যামেলিয়া ফুল লাগানো হয়। কারণ চা ক্যামেলিয়ার নিকটাত্মীয়। উষ্ণ, আর্দ্র আবহাওয়ায় পানি জমে না এমন ঈষৎ ঢালু ভূমিতেই চা গাছ ভালো জন্মে। এর জন্য আদর্শ উচ্চতা হলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯শ থেকে ২ হাজার মিটার। এরকম উচ্চতায় চা-গাছ বাড়ে ধীরে, কিন্তু স্বাদ হয় ভালো। চা গাছকে অবাধে বাড়তে দিলে ৯ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কিন্তু বাগানে একে ছেঁটে মাত্র ১ মিটারের মতো উচ্চতায় রাখা হয়। নতুন চারা ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে চা দিতে পারে। এ সময় তা থেকে দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ির সমন্বয়ে নিত্যনতুন কচি শাখা বের হতে থাকে।
চা-পানের প্রথম খোঁজ পাওয়া যায় ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে রচিত চীনা সাহিত্যে। চীনে এর বহু আগে থেকেই চা প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। সারা বিশ্বে মাথাপিছু সর্বাধিক চা-পানের পরিমাণ দেখা যায় আয়ারল্যান্ডে বছরে জনপ্রতি ১৬০০ কাপ। তার পরেই ব্রিটেন আর নিউজিল্যান্ডের স্থান। আর সবচেয়ে বেশি চা উৎপন্ন হয় ভারত ও চীনে। পরবর্তী অবস্থানে আছে শ্রীলঙ্কা, রাশিয়া, বাংলাদেশ, কেনিয়া ও ইন্দোনেশিয়া। চা-বাগানে বেড়াতে গেলে দেখে যেমন সুখ তেমনি চা-পানেও পাওয়া যাবে তৃপ্তি।
কমলা
সিলেটের কমলা নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে। আগে ছাতকের গল্পটাই বলি। সবার ধারণা সিলেটের ছাতক কমলার জন্য বিখ্যাত। বাস্তবেও কী সেখানে এত কমলার চাষ হতো? অনুসন্ধানে তার সত্যতা মেলেনি। বিজ্ঞান লেখক অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মার শৈশব-কৈশোর কেটেছে জন্মস্থান বড়লেখায়। তিনি জানিয়েছেন ছাতকে আদতে কোনো কমলার চাষ হতো না। অদূরে ভারতের খাসিয়া পাহাড়ে প্রচুর কমলা হতো। সেখান থেকে এ পথে কমলা আসত সিলেটে। আর সে কমলাই ছাতকের বলে চালিয়ে দেওয়া হতো। কমলা নিয়ে আরেকটি গল্পও প্রচলিত ছিল। সিলেটের কমলা প্রথমে সীমান্ত পথে ভারত যায়। সেখান থেকে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে আবার বাংলাদেশে আসে। কোন খবরটা বিশ্বাসযোগ্য? তবে সিলেটে কমলার চাষ যে একেবারেই হয়নি তা নয়, হয়েছে সীমিত পরিসরে। কিন্তু হঠাৎ করেই গত কয়েক বছর দীর্ঘ নিদ্রার পর জেগে ওঠে কমলা গ্রামগুলো। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয় একাধিক প্রতিবেদন। কমলা বাগানগুলোতে ফিরে আসে প্রাণচাঞ্চল্য।
বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে কমলা চাষ হয় এমন বাগানের সংখ্যা প্রায় চার শ। ২০০৮ সালে সবচেয়ে বেশি কমলা হয়েছে জুড়ী-কুলাউড়া এলাকায়। হেক্টরপ্রতি ফলন প্রায় ১৩ হাজার। বিভিন্ন বাগান ঘুরে ও কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, বৃহত্তর সিলেটের কমলা আনারস উন্নয়নসহ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ৬০ হেক্টর ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২০ হেক্টরসহ মোট ৮০ হেক্টরজুড়ে কমলা বাগান রয়েছে। জুড়ী উপজেলার গোয়ালবাড়ি, দিলকুশ, কচুরগুল, লাঠিটিলা, সাগরনাল, বড়ডহর, বাছিতপুর, জায়ফরনগর, বাহাদুরপুর এবং কুলাউড়া উপজেলার ফটিগুলি, গোয়ালগ্রাম, ইছাচড়া, মুরইচড়া, টাট্রিউলি, পৃথিমপাশা ও গণকিয়া এলাকার পাহাড়ি মাটি অম্ল হওয়ায় কমলা চাষের উপযোগী। এসব এলাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় ২ সহস্রাধিক চাষি কমলা উৎপাদনে রাতদিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তবে বিয়ানীবাজারের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। প্রথম দিকে কৃষি কর্মকর্তারা সেখানে নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করলেও পরবর্তী সময়ে তাদের তেমন কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া কৃষকদের মধ্যে নিম্নমানের চারা বিতরণের অভিযোগও রয়েছে। তবুও জলঢুপ এলাকায় নিজ উদ্যোগে করা কয়েকটি বাগানে ২০০৮ সালে ভালো ফলন হয়েছে। প্রায় প্রতি বাগান থেকেই লক্ষাধিক টাকার কমলা বিক্রি করা হয়।
ধারণা করা হয়, কমলার আদিআবাস চীন। সারা বিশ্বে অসংখ্য জাতের কমলা হলেও আমাদের দেশে মাত্র কয়েক জাতের কমলা দেখা যায়। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উন্নত ফলনশীল বারি-১ নামের একটি নতুন জাত আবিষ্কার করেছে। খাসিয়া জাতের কমলার ওজন ১৪০-২২৪ গ্রাম, নাগপুরী জাতের ওজন ১১২-১৬৮ গ্রাম ও বারি কমলা ১৮০-২০০ গ্রাম ওজনের হয়। কমলা গাছ আর বাতাবি লেবু গাছ প্রায় একই রকম। কমলা গাছের শাখা-প্রশাখা ছড়ানো প্রায় ৬ মিটার উঁচু। পাতা কিঞ্চিত বাঁকা, ডিম্বাকৃতি ও অগ্রভাগ মোটা। ফুল সাদাটে, উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। ফল গোলাকার, উভয় দিকে খানিকটা চাপা। গা মসৃণ, খোসার আবরণের ভেতর টক-মিষ্টি স্বাদের কোষ থাকে। কমলার পুষ্টি ও ঔষধি গুণ অনেক। প্রতি একশ ভাগ ফলে থাকে ০.৯ ভাগ প্রোটিন, ০.৩ ভাগ সহজপ্রাচ্য ফ্যাট, ১০.৪ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ০.৪ ভাগ খনিজ পদার্থ, ০.৫ ভাগ ক্যালসিয়াম, ০.২ ভাগ ফসফরাস, ০.১ ভাগ লৌহ ও প্রতি ১০০ গ্রামে ভিটামিন ‘এ’ থাকে ৩৫০ আই.ইউ, বি-১ থাকে ১২০ মিলিগ্রাম ও ‘সি’ থাকে ৬৮ মি.গ্রা। তাছাড়া প্রতি কেজি ফলে ৪৯০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। কমলার তাজা খোসা, শুকনো খোসা, পাতা, ফুলের নির্যাস-সবকিছুই নানা অসুখে ব্যবহার্য। পাতা ও ফলের খোসা থেকে তৈরি হয় সুগন্ধি তেল। বংশবৃদ্ধি বীজ ও কলমে।
দুলিচাঁপা
দুলিচাঁপা আমাদের একমাত্র বুনো ম্যাগনোলিয়া। ফোটে মৌলভীবাজার জেলার পাথারিয়া পাহাড়ে। দু®প্রাপ্য এই ফুলটির সন্ধান পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া আমাদের অন্য কোনো পাহাড়ে আছে কি না জানা নেই। চিরসবুজ বড় গাছ। মাথা গোলাকার, পাতা বড়, ২০ থেকে ৩৫ সেমি, মাথার দিক চওড়া, বোঁটার দিকে সরু চার্ম ও মসৃণ, আগা ভোঁতা, বোঁটা খাটো। ডালের আগায় পুরুষ্টু বোঁটায় একটি ফুল। ফুল বড় ১০ সেমি চওড়া, সাদা ও সুগন্ধি। পাপড়ি সংখ্যা ৬, ডিম্বাকৃতি, পুরুষ্টু। ফলগুচ্ছ ১২ থেকে ১৮ সেমি লম্বা, ৪ থেকে ৬ সেমি চওড়া। ছোট ছোট ফলের আগা সামান্য লম্বা ও চোখা। বীজ কমলা রঙের। ফুল ফোটে গ্রীষ্মে। বৈজ্ঞানিক নাম Magnolia pterocarpa.
দাঁতরাঙা (বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড়)
সিলেটের পাহাড়ি এলাকায় যত্রতত্র যে ফুলটি প্রায় সারা বছর দেখা যায় তার নাম দাঁতরাঙা বা লুটকি। তবে সিলেট ছাড়া এটি পঞ্চগড়, গাজীপুর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামেও দেখা যায়। পাহাড়ের ঢালু ও আশপাশের পতিত স্থানে প্রচুর জন্মে। সাধারণত পাহাড় বা লালমাটি অঞ্চল ছাড়া দেশের অন্য কোথাও চোখে পড়ে না। সাদা ও বেগুনি রঙের মধ্যে বেগুনি রঙটাই বেশি চোখে পড়ে। পাতা চকচকে সবুজ, শিরা সুস্পষ্ট। এরা বাংলাদেশ ও ভারতের প্রজাতি। ঝোপাল গাছ, ১ থেকে ২ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। পাতা ডিম্ব-আয়তাকার, রোমশ, তাতে সমান্তরাল শিরা। প্রায় সারা বছরই ফুল। ডালের আগায় অল্প কয়েকটি ফুল গুচ্ছবদ্ধ থাকে। ফুল বড়, ৫ থেকে ৬ সেমি চওড়া, গন্ধহীন। মাঝখানে হলুদ ও বেগুনি রঙের অসমান কয়েকটি পুংকেশর আছে। ফল ডিম্বাকার। বীজ খুব ছোট, কালো শাঁসে জড়ানো। বীজ ও কলমেই চাষ। সিলেটে স্থানীয় নাম লুটকি। বৈজ্ঞানিক নাম Melastoma malabathricum.
সুলতানচাঁপা (উপকূলীয় জেলা)
অঞ্চলভেদে এ ফুলটির অনেক নাম সুলতানচাঁপা, কন্ন্যাল, পুন্ন্যাগ ইত্যাদি। আমাদের উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেশ সহজলভ্য ছিল। ইদানীং নানা কারণে সংখ্যায় কমেছে। ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপের প্রজাতি। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ব্যতীত চট্টগ্রামের বনাঞ্চলেও থাকতে পারে। এদের খুবই ঘনিষ্ঠ প্রজাতি কামদেব পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম বনজ দারুবৃক্ষ। গাছ সুশ্রী, চিরসবুজ, লম্বাটে গড়ন, সাধারণত ১২ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। পাতা ৮ থেকে ১৬ সেমি পর্যন্ত লম্বা, আগা গোল। স্থানানুসারে ফুল ফোটে গ্রীষ্মের শেষ, বর্ষা বা শীতে, পাতার কোলে ১০ থেকে ১৫ সেমি লম্বা শাখায়িত মঞ্জরিতে ছোট ছোট সুগন্ধি সাদা ফুলগুলো পর্যায়ক্রমে ফোটে। ৪ গুচ্ছের পুংকেশর হলুদ রঙের। ফল শাঁসাল, গোলাকার ৩-৪ সেমি চওড়া ও হলুদ। বংশবৃদ্ধি বীজ ও কলমে। বৈজ্ঞানিক নাম Calophyllum inophyllum
কেয়াবন (কক্সবাজার)
কেয়া বর্ষার অন্যতম প্রধান ফুল। কিন্তু নগর নিসর্গে তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে। কেয়াবন পাবেন উপকূলীয় দ্বীপগুলোতে। বিশেষ করে কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন, মহেশখালী ও সোনাদিয়ায় প্রচুর কেয়া বন আছে। সৈকতের বালিয়াড়ির ক্ষয়রোধেও স্থানীয়ভাবে কেয়াগাছ লাগানো হয়। কেয়ার অন্য নাম কেতকী। রবীন্দ্রনাথ তার মধুর সুগন্ধ চুলে মাখার কথা গানে বেঁধেছেন।
‘কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী।’
কেয়ার গন্ধ গভীর ও মাদকতাপূর্ণ। গন্ধে পাগল হয়ে ভ্রমরদল ছুটে যায়। কিন্তু কেয়া ফুলে মধু নেই, আছে কাঁটায় ভরা লম্বা পাতার রাশি। ফুলেল গর্ভ পরাগে ভরা, তাতে মধু নেই, ভোমরা ওই পরাগের লোভে ছুটে এসে তাতে মাখামাখি করে চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে। কেয়া সুগন্ধি কুসুম কিন্তু গাছ ছিন্নরুহা। সাদা ও সোনালি রঙের পাতাভেদে এরা দু রকম। গাছ ১০ থেকে ১৫ ফিট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কা- থেকে শাখা-প্রশাখা ও শেকড়ের ঝুরি বের হয়। পাতা ৫-৭ ফিট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। কিনারা করাতের দাঁতের মতো কাটা কাটা। অনেকটা আনারস পাতার মতো। কা- ও ঝুরিগুলো শক্ত ও গোলাকার। ফুল সাদা ও ঝুলন্ত। একটি শক্ত ব্রাকটের ভেতরে থেকে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়। ফল ৭-৮ ইঞ্চি লম্বা, রঙ কমলা ও পীত ধূসর এবং শক্ত ও গোলাকার। এ গাছ ঔষধি গুণে ভরা। কা-, ফুল, দ-, বীজ ও ঝুরির দ- বিভিন্ন ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। বৈজ্ঞানিক নাম Pandanus odoratissimus.
শটি (টাঙ্গাইল ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ)
শাল-গজারি বন একসময় ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর এ বনের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল শটিসহ নানাজাতের ফুল ফল ও লতাগুল্ম। আমাদের বর্বরতায় শালবন এখন বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে ঠেকেছে। তবুও হঠাৎ দু-একটি শটি কিংবা কেও ফুল আমাদের চমকে দেয়। সারা দেশে কম বেশি চোখে পড়লেও শটি পুরনো ও লালমাটি অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। এ ফুল মুগ্ধ হওয়ার মতো সুশ্রী। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে খোলা জায়গায় যেখানে শুধু মোটা ঘাস ছাড়া কিছুই নেই সেখানে হলদে মাথা ছোট্ট ডাটির ওপর শটি ফুল দুর্লভ সৌন্দর্য ছড়ায়। বৈশাখে নতুন পাতা গজাবার আগে এ ফুল দেখা দেয়, আবার কিছু পাতা বের হওয়ার পরও দেখা যায়। পাতা ২ থেকে ৩ ফিট লম্বা দেখতে অনেকটা হলুদ গাছের পাতার মতো। গোড়ার মূল বা কন্দটি দেখতে হলুদের মতো। এর নামই শটি। বিশেষ পদ্ধতিতে এর নির্যাসটুকু চটকে নিলে ময়দার মতো একটি দ্রব্য পাওয়া যায়। এক সময় এর থেকে আবীর হতো। তখন আবীর তৈরি প্রায় কুটির শিল্পের পর্যায়ে ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও এর ব্যাপক চাহিদা ছিল। শটির কন্দ সুগন্ধযুক্ত। এক সময় রান্না করে বার্লির মতো করে রোগীদের খাওয়ানো হতো। তাছাড়া দুধ-চিনি দিয়ে চমৎকার পায়েসও করা যায়। শটি বিভিন্ন রোগের মহৌষধ হিসেবেও কাজে লাগে। তবে এখন আর শটির বহুমাত্রিক ব্যবহার নেই। বৈজ্ঞানিক নাম Curcuma aromatica.
কাইজেলিয়া পিনাটা ( রংপুর)
রংপুর কারমাইকেল কলেজ প্রাঙ্গণে কাইজেলিয়ার প্রায় শতবর্ষী দুটো গাছ আছে। সেই অর্থে গাছটি দুর্লভ। একসময় এই দুটি গাছই ছিল আমাদের দেশে। ইদানীং উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের নিরন্তর চেষ্টায় কলম পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক গার্ডেনসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যানে কাইজেলিয়ার কিছু চারাকলম লাগানো হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, কলেজ প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯২০ সালের দিকে গাছ দুটো রোপণ করা হয়। কয়েক বছর আগে গাছ দুটি স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি করলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রকৃত পরিচয় জানতে সঠিক শনাক্তির জন্য কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি বংশবৃদ্ধির জন্যও গবেষণা করেন। অবশেষে তারা এই গাছটিকে কাইজেলিয়া পিনাটা হিসেবে শনাক্ত করেন এবং তার বংশ বৃদ্ধি করতেও সক্ষম হন।
এই গাছ প্রায় ৭০ মিটার উঁচু হতে পারে। কা-, ডালপালা সবই শক্ত, ঝুলন্ত, পাতা চর্মবৎ, খসখসে, যৌগপত্র বিজোড়, পত্রিকা ৪ ইঞ্চি লম্বা। বেগুনি রঙের ফুলগুলো ফোটে ভাদ্র মাসে, থাকে আশ্বিন-কার্তিক অবধি। এরা নিশিপুষ্প, লম্বায় ৪ ইঞ্চি, ব্যাস ৫ ইঞ্চি। গড়ন অনেকটা কানাইডিঙা কিংবা শোলার মতো। পুংকেশর ৪টি, গন্ধহীন; পরাগকেশর গাছেই থেকে যায়। জন্মস্থানে ফল থেকে বংশবৃদ্ধি সম্ভব হলেও আমাদের দেশে তা সম্ভব হয়নি। সেখানে এক ধরনের বাদুড় পরাগায়নের কাজটি করে। ফল ১১-১২ ইঞ্চি লম্বা, লম্বাটে গড়ন, পরিণত খিরাইয়ের মতো ধূসর ফাটা ফাটা। পুরনো ফল ঝরে পড়ার আগেই নতুন ফল আসে। এ কারণে সারা বছর গাছে কমবেশি ফল দেখা যায়। ফলের এমন আকৃতির কারণে গাছটির আরেক নাম শেল প্ল্যান্ট। তবে সসেজ ট্রি নামেও গাছটি পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নাম Kigelia pinata । তবে রংপুর শহরের আরেকটি বিশেষত্ব আছে। শহরটি বুদ্ধনারকেলের জন্য বিখ্যাত। এত বুদ্ধনারকেলের গাছ আর কোনো শহরে দেখা যায় না।
লিলিয়াম (যশোর)
বাংলাদেশে একমাত্র লিলিয়াম চাষ হয় যশোর জেলার টাওরা গ্রামে। তাও বেশি দিন আগের কথা নয়। নতুন এই ফুলটি কিভাবে চাষ করা হচ্ছে তা সবিস্তারে জানার জন্য গিয়েছিলাম সেখানে। যশোর ও বেনাপোলের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে গদখালী বাজার। ফুলের হাট হিসেবে এই বাজারের খ্যাতি আছে। বাজার থেকে ভ্যানে চেপে টাওরা গ্রামে যাওয়ার পথে দেখি চাষিরা গোলআলু বস্তায় ভরছেন। এই সব আলু বিভিন্ন হিমাগারে চলে যাবে। আশপাশে আরো শাক-সবজি দেখে আমার ধারণা কিছুটা পাল্টে গেল। এখানে শুধু ফুল নয়, শাক-সবজিও হয়। এ সবের ফাঁকে ফাঁকেই চোখে পড়ল গ্ল্যাডিওলাস, গাঁদা ও গোলাপের খেত। একসময় ব্যাপক রজনী গন্ধার চাষ হলেও এখন আর খুব একটা হয় না। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনেই ফুটেছে রক্তিম শিমুল। এসব দেখতে দেখতেই একসময় চলে আসি মো. দুলাল সরকারের বাড়িতে। তখন মধ্যদুপুর। দুলাল সরকার ঘরের আঙিনায় কাজের তদারকি করছিলেন। উঠানে ছড়িয়ে আছে গোলাপ আর গ্ল্যাডিওলাস। এ সব ফুল প্রক্রিয়া শেষে বিভিন্ন বাজারে চলে যাবে।
ফাল্গুনের দুপুরের রোদটা একটু মরে গিয়ে যখন বিকেল নামল তখন দুলাল সরকারকে সঙ্গে নিয়ে
লিলিয়াম Kigelia pinata দেখতে গেলাম। বাড়ির দক্ষিণ পাশে ৮ কাঠা জায়গার ওপর তিনি লিলিয়াম চাষ করেছেন। বেশ কিছু ফুল ইতিমধ্যে বিক্রিও হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকিগুলোও বিক্রি করবেন। বাংলাদেশে এই প্রথম আনুষ্ঠানিক লিলিয়াম চাষ। বর্ণবৈচিত্র্য, দীর্ঘস্থায়িত্ব ও সুগন্ধের জন্য লিলিয়ামের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই ফুলটির চাষ করেছেন দুলাল সরকার। কারণ বীজ বোনার আগেও তিনি জানতেন না, এই বীজ থেকে চারা হবে কি না, ফুল হবে কি না। তবে ভালোয় ভালোয় ফুল ফোটার পর তার সেই দুশ্চিন্তা অনেকটাই কেটে গেছে।
বাগান ঘুরে ঘুরে ফুল দেখতে দেখতে জানা গেল বৃত্তান্ত। প্রথমে ভারত থেকে ৪ হাজার কন্দ কেনা হয় চাষের জন্য। সেখান থেকে প্রতিবেশী ফুলচাষি আবদুর রহিম ১ হাজার কন্দ নিয়ে যান। এসব কন্দ এসেছে সরাসরি হল্যান্ড থেকে। তারপর ২০০৮ সালের ৪ ডিসেম্বর তিনি বীজগুলো বুনে দেন। মাত্র দু মাসের ব্যবধানেই ফুল ফুটতে শুরু করে। তবে প্রস্ফুটন মৌসুম পর্যন্ত প্রতিটি ধাপই বেশ সতর্কতার সঙ্গে অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রথমেই ভালোভাবে প্রস্তুত করতে হয়েছে জমি। পর্যায়ক্রমে সার, কীটনাশক ও সেচ করতে হয়েছে। চাষ পদ্ধতি অন্যান্য ফুলের মতোই, বাড়তি কোনো যত্ন-আত্তির প্রয়োজন নেই। এ বছর ৭-৮ ভ্যারাইটির লিলিয়াম চাষ করেছেন দুলাল। সাদা, লাল, হলুদ কত রঙের বাহার! সারা বিশ্বে প্রায় ৯০ ধরনের লিলিয়াম পাওয়া যায়।


 Reporter Name
Reporter Name