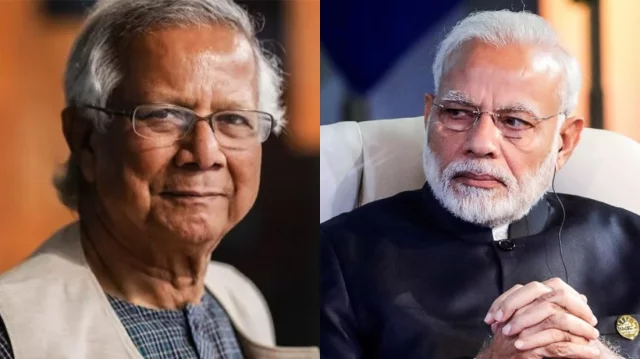প্রকৃতি ধ্বংস করে নগরায়ণ এবং প্রকৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভবন তৈরির কারণে শহর ও গ্রামের তাপমাত্রার পার্থক্য তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে।
প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা যেকোনো গ্রামের সঙ্গে রাজধানীর দিনের তাপমাত্রার পার্থক্য ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবার সন্ধ্যায় শহরের ফ্ল্যাটবাড়ির বাইরের অংশের চেয়ে ভেতরের তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।
বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক খন্দকার সাব্বির আহমেদ ১৫ বছর ধরে এ বিষয়ে গবেষণা করছেন। শহরে তপ্ত ভূখণ্ড তৈরির নানা কারণ হিসেবে গাছপালা ও জলাশয় ধ্বংস করে অপরিকল্পিত নগরায়ণের বিষয়টি চিহ্নিত করেছেন তিনি। গত বছর থেকে শুরু হওয়া আরেকটি গবেষণায় সাব্বির আহমেদের তত্ত্বাবধানে ওই বিভাগেরই দুজন শিক্ষক ঢাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক কারণ চিহ্নিত করেছেন। এতে রাজধানীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে প্রকৃতি ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ভবন নকশা পরিবেশবান্ধব না হওয়াকে দায়ী করা হয়েছে।
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাইফুল ইসলাম ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকার তাপমাত্রা নিয়ে পিএইচডি গবেষণা করেন। এতে দেখা যায়, ভবন নকশার কারণে ঘরের ভেতরে ও বাইরের তাপমাত্রার পার্থক্য ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হয়। তাঁর গবেষণাতেই বেরিয়ে আসে, রাজধানীর সঙ্গে একটি গ্রামের তাপমাত্রার পার্থক্য অন্তত ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
যেকোনো এলাকার তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করলেই আবহাওয়াবিদরা তাকে দাবদাহ বলেন। গত সোমবার রাজধানীর তাপমাত্রা ছিল ৩৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে এই তাপমাত্রা আবহাওয়া দপ্তর মেপেছে রাজধানীর আগারগাঁও ও হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায়। সেখানকার গড় তাপমাত্রা শহরের অন্য এলাকার চেয়ে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সেই হিসাবে এক সপ্তাহ ধরেই ঢাকার বেশির ভাগ এলাকার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশিই ছিল, যা মাঝারি তীব্রতার দাবদাহের সমান।
এ ব্যাপারে বিশিষ্ট পরিবেশবিজ্ঞানী ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আইনুন নিশাত বলেন, ঢাকার নগরায়ণের ওপর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানে দুই ভবনের মাঝখানে কোনো জায়গা রাখা হচ্ছে না। ফলে আলো-বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শহরটা কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বাড়িঘর ও অফিসে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসছে। এগুলো ঘরের বাইরে তাপ বের করে দিচ্ছে। ফলে বাড়ির বাইরে তাপ আরও বাড়ছে।
টেক্সাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ঢাকায় বায়ুর আরাম ও ধরন’ শীর্ষক ২০১১ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, রাজধানীর ভবনগুলো এমনভাবে তৈরি হচ্ছে যে সেখানে আলো-বাতাস কম প্রবেশ করছে। নব্বইয়ের দশকে রাজধানীর বেশির ভাগ ভবনের প্রতিটি ফ্লোর বা তলার মেঝে থেকে ছাদের উচ্চতা ছিল ১১ থেকে ১৩ ফুট। ২০০০ সালের পর থেকে প্রতিটি তলার উচ্চতা কমে সাড়ে ৯ ফুট করা হচ্ছে। আগের ভবনগুলোর ছাদে ও জানালায় কার্নিশ দেওয়ার চল ছিল। এখনকার ভবনে তা উঠেই গেছে। ফলে বাইরের তাপ প্রতিটি ভবনকে একেকটি অগ্নিচুল্লিতে পরিণত করছে।
ওই গবেষণাতেই দেখা গেছে, ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর রান্নাঘর ও টয়লেট এমনভাবে নির্মিত হচ্ছে যে সেখানকার তাপ বাইরে বের না হয়ে ঘরের মধ্যেই আটকে থাকছে। ঘরে আলো না থাকায় সারা দিন বাতি জ্বালিয়ে রাখা হচ্ছে। ঘরের তাপ কমাতে অনেকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করছেন। এতে ঘর ঠাণ্ডা থাকছে ঠিকই, কিন্তু শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র থেকে বের হওয়া তাপের কারণে ভবনের বাইরের তাপমাত্রা বাড়ছে, যা ভবনটিকেই আরও উত্তপ্ত করে তুলছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক সমরেন্দ্র কর্মকার দেশের তাপমাত্রার গতি-প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি রাজধানীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির হারকে আশঙ্কাজনক হিসেবে তুলে ধরে বলেন, নব্বইয়ের দশকের পর থেকে রাজধানীতে অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসের কারণে তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে।
ঘরের ভেতরে তাপমাত্রা আটকে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাইফুল ইসলাম বলেন, ১৯৯৬ সালের আগে রাজধানীর যেসব ভবন নির্মিত হতো, তার বড়জোর ২০ শতাংশ খালি রাখা হতো। শীতপ্রধান দেশগুলোর ভবন নির্মাণ অন্ধভাবে অনুসরণ করায় রাজধানীর ফ্ল্যাট বাড়িগুলো থেকে বাতাস প্রবাহের জায়গা বা ভেন্টিলেটর উঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালের আগে ভবনগুলোর ভেতরে প্রতি ঘণ্টায় ১২ বার বাতাস প্রবাহিত হতো। কিন্তু ২০০৮ সালে নতুন ভবন নির্মাণ আইন অনুসরণ করে যাঁরা ভবন তৈরি করেছেন, তাঁদের ঘরে ঘণ্টায় ২২ বার বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু বাতাসের গতিবেগ ও প্রবাহের ধরন মাথায় রেখে যাঁরা ভবন তৈরি করেছেন, তাঁদের ঘরে বাতাস বইছে ৩০ বার।
সাইফুল ইসলামের মতে, ঘরের বাইরের তাপ ও ভেতরে তৈরি হওয়া উত্তাপ মিলেমিশে রাজধানীতে গ্রীষ্মের স্বাভাবিক তাপমাত্রাই দাবদাহের মতো করে অনুভূত হচ্ছে। বাতাস ও আলো চলাচলের যথেষ্ট স্থান রাখার ব্যবস্থা রেখে নতুন ভবন নির্মাণের পরামর্শ দেন তিনি।
প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা যেকোনো গ্রামের সঙ্গে রাজধানীর দিনের তাপমাত্রার পার্থক্য ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবার সন্ধ্যায় শহরের ফ্ল্যাটবাড়ির বাইরের অংশের চেয়ে ভেতরের তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।
বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক খন্দকার সাব্বির আহমেদ ১৫ বছর ধরে এ বিষয়ে গবেষণা করছেন। শহরে তপ্ত ভূখণ্ড তৈরির নানা কারণ হিসেবে গাছপালা ও জলাশয় ধ্বংস করে অপরিকল্পিত নগরায়ণের বিষয়টি চিহ্নিত করেছেন তিনি। গত বছর থেকে শুরু হওয়া আরেকটি গবেষণায় সাব্বির আহমেদের তত্ত্বাবধানে ওই বিভাগেরই দুজন শিক্ষক ঢাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক কারণ চিহ্নিত করেছেন। এতে রাজধানীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে প্রকৃতি ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ভবন নকশা পরিবেশবান্ধব না হওয়াকে দায়ী করা হয়েছে।
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাইফুল ইসলাম ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকার তাপমাত্রা নিয়ে পিএইচডি গবেষণা করেন। এতে দেখা যায়, ভবন নকশার কারণে ঘরের ভেতরে ও বাইরের তাপমাত্রার পার্থক্য ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হয়। তাঁর গবেষণাতেই বেরিয়ে আসে, রাজধানীর সঙ্গে একটি গ্রামের তাপমাত্রার পার্থক্য অন্তত ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
যেকোনো এলাকার তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করলেই আবহাওয়াবিদরা তাকে দাবদাহ বলেন। গত সোমবার রাজধানীর তাপমাত্রা ছিল ৩৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে এই তাপমাত্রা আবহাওয়া দপ্তর মেপেছে রাজধানীর আগারগাঁও ও হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায়। সেখানকার গড় তাপমাত্রা শহরের অন্য এলাকার চেয়ে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সেই হিসাবে এক সপ্তাহ ধরেই ঢাকার বেশির ভাগ এলাকার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশিই ছিল, যা মাঝারি তীব্রতার দাবদাহের সমান।
এ ব্যাপারে বিশিষ্ট পরিবেশবিজ্ঞানী ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আইনুন নিশাত বলেন, ঢাকার নগরায়ণের ওপর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানে দুই ভবনের মাঝখানে কোনো জায়গা রাখা হচ্ছে না। ফলে আলো-বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শহরটা কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বাড়িঘর ও অফিসে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসছে। এগুলো ঘরের বাইরে তাপ বের করে দিচ্ছে। ফলে বাড়ির বাইরে তাপ আরও বাড়ছে।
টেক্সাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ঢাকায় বায়ুর আরাম ও ধরন’ শীর্ষক ২০১১ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, রাজধানীর ভবনগুলো এমনভাবে তৈরি হচ্ছে যে সেখানে আলো-বাতাস কম প্রবেশ করছে। নব্বইয়ের দশকে রাজধানীর বেশির ভাগ ভবনের প্রতিটি ফ্লোর বা তলার মেঝে থেকে ছাদের উচ্চতা ছিল ১১ থেকে ১৩ ফুট। ২০০০ সালের পর থেকে প্রতিটি তলার উচ্চতা কমে সাড়ে ৯ ফুট করা হচ্ছে। আগের ভবনগুলোর ছাদে ও জানালায় কার্নিশ দেওয়ার চল ছিল। এখনকার ভবনে তা উঠেই গেছে। ফলে বাইরের তাপ প্রতিটি ভবনকে একেকটি অগ্নিচুল্লিতে পরিণত করছে।
ওই গবেষণাতেই দেখা গেছে, ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর রান্নাঘর ও টয়লেট এমনভাবে নির্মিত হচ্ছে যে সেখানকার তাপ বাইরে বের না হয়ে ঘরের মধ্যেই আটকে থাকছে। ঘরে আলো না থাকায় সারা দিন বাতি জ্বালিয়ে রাখা হচ্ছে। ঘরের তাপ কমাতে অনেকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করছেন। এতে ঘর ঠাণ্ডা থাকছে ঠিকই, কিন্তু শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র থেকে বের হওয়া তাপের কারণে ভবনের বাইরের তাপমাত্রা বাড়ছে, যা ভবনটিকেই আরও উত্তপ্ত করে তুলছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক সমরেন্দ্র কর্মকার দেশের তাপমাত্রার গতি-প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি রাজধানীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির হারকে আশঙ্কাজনক হিসেবে তুলে ধরে বলেন, নব্বইয়ের দশকের পর থেকে রাজধানীতে অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসের কারণে তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে।
ঘরের ভেতরে তাপমাত্রা আটকে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাইফুল ইসলাম বলেন, ১৯৯৬ সালের আগে রাজধানীর যেসব ভবন নির্মিত হতো, তার বড়জোর ২০ শতাংশ খালি রাখা হতো। শীতপ্রধান দেশগুলোর ভবন নির্মাণ অন্ধভাবে অনুসরণ করায় রাজধানীর ফ্ল্যাট বাড়িগুলো থেকে বাতাস প্রবাহের জায়গা বা ভেন্টিলেটর উঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালের আগে ভবনগুলোর ভেতরে প্রতি ঘণ্টায় ১২ বার বাতাস প্রবাহিত হতো। কিন্তু ২০০৮ সালে নতুন ভবন নির্মাণ আইন অনুসরণ করে যাঁরা ভবন তৈরি করেছেন, তাঁদের ঘরে ঘণ্টায় ২২ বার বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু বাতাসের গতিবেগ ও প্রবাহের ধরন মাথায় রেখে যাঁরা ভবন তৈরি করেছেন, তাঁদের ঘরে বাতাস বইছে ৩০ বার।
সাইফুল ইসলামের মতে, ঘরের বাইরের তাপ ও ভেতরে তৈরি হওয়া উত্তাপ মিলেমিশে রাজধানীতে গ্রীষ্মের স্বাভাবিক তাপমাত্রাই দাবদাহের মতো করে অনুভূত হচ্ছে। বাতাস ও আলো চলাচলের যথেষ্ট স্থান রাখার ব্যবস্থা রেখে নতুন ভবন নির্মাণের পরামর্শ দেন তিনি।
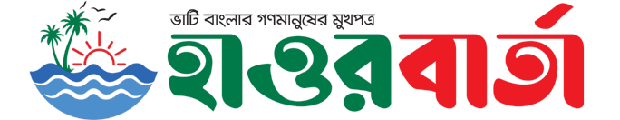
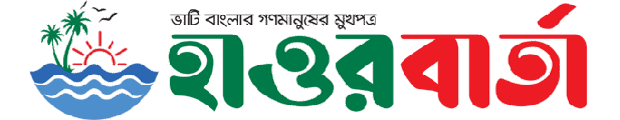
 Reporter Name
Reporter Name