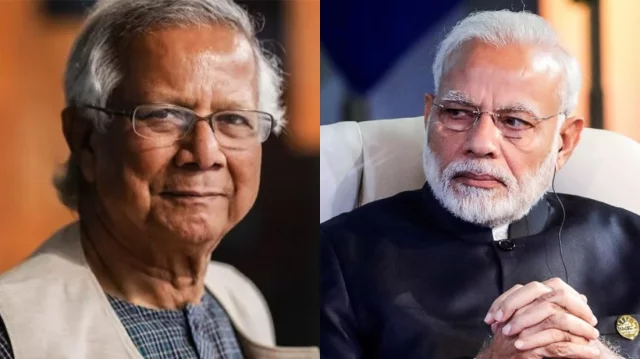গত কয়েক বছর হলো, ঈদের বেশ কিছুদিন আগে থেকে শুরু করে ঈদ শেষ হওয়ার বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত আমি এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি। আমার ধারণা, আমি একা নই, আমার মতো আরো অনেকের ভেতরেই এই ভীতিটা কাজ করে। ঈদের আগে আমি ভয়ে ভয়ে থাকি। কারণ মনে হতে থাকে, যেকোনো দিন আমি খবরে দেখব, জাকাত নিতে গিয়ে মানুষ পায়ের চাপায় মারা যাচ্ছে। ঈদের পর ভয়ে ভয়ে থাকি। কারণ মনে হতে থাকে, খবরে দেখব, ঈদের ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার সময় কিংবা ছুটি শেষে ফিরে আসার সময় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট বা লঞ্চডুবিতে মানুষ মারা যাচ্ছে। আমার মনে হয়, এই বছরটা বাড়াবাড়ি রকমের খারাপ ছিল। এই দেশে এখন একটা শাড়ি বা লুঙ্গির জন্য একজনের জীবন দেওয়ার অবস্থা নেই। তার পরও একজন-দুজন নয়, ২৭ জন মানুষ এই বছর জাকাতের শাড়ি-লুঙ্গির জন্য প্রাণ দিয়েছে। আর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে ঈদের ছুটিতে এই বছর যত মানুষ মারা গেছে, সেটি যেকোনো হিসাবে ভয়ংকর। আমি যদিও অ্যাক্সিডেন্ট (বা দুর্ঘটনা) শব্দটা ব্যবহার করেছি; কিন্তু আমরা সবাই জানি, কোনো হিসাবেই এগুলো অ্যাক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনা নয়। যে ‘ঘটনা’ এড়ানো সম্ভব, সেটা মোটেও দুর্ঘটনা নয়। যদি এই দেশের মানুষ শুধু খুবই সহজ; কিন্তু নিয়মকানুন মেনে চলত, তাহলে এ রকম সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমিয়ে নিয়ে আসা যেত, আমাদের দেশে যারা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে তারা সবাই এই কথা স্বীকার করবে।
ঢাকা গেলে আমি যেখানে থাকি সেটি ট্রেন লাইনের খুব কাছে, আমি বাসার বারান্দা থেকে প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি ট্রেনকে যেতে কিংবা আসতে দেখি। ঈদের ঠিক আগে আগে এই ট্রেনগুলো দেখলে মাথা ঘুরে যায়, তখন ট্রেনের কাঠামোটাও দেখা যায় না, মানুষ এবং মানুষে সেটা ঢেকে থাকে। ট্রেনের ছাদে শুধু যে দুঃসাহসী কিছু মানুষ থাকে তা নয়, সেখানে শিশু থাকে এবং মহিলাও থাকে। এবারের যাত্রাটি অন্যবার থেকে ভিন্ন ছিল। কারণ যারা সেখানে বসেছিল তারা নিশ্চিতভাবে প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তাদের যাত্রাটি শেষ করেছে।
একজন মানুষ ঈদের ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার জন্য কেমন করে এত বড় ঝুঁকি নেয়, আমি সেটি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারি না। কারণ আমি নিজে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন ট্রেনের ভেতরে খুব বেশি ভিড় ছিল বলে ট্রেনের ছাদে বসে মহানন্দে ভ্রমণ করেছি। ট্রেনের ছাদে দাঁড়িয়ে যখন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছি তখন নিচে দাঁড়ানো কিছু মানুষ আতঙ্কিত হয়ে হাত নেড়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল-তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে চোখ ফেরানোর কারণে নিচু হয়ে ঝুলে থাকা ইলেকট্রিক তারটা চোখে পড়েছিল এবং শেষ মুহূর্তে বসে পড়ার কারণে সেই তারের আঘাতে ট্রেনের ছাদ থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটি পেতে হয়নি! আমার জীবনে এ রকম নির্বুদ্ধিতার তালিকা অনেক দীর্ঘ! একাত্তরে আমি ও বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ মা ও অন্য ভাই-বোন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছিলাম, কখনো হেঁটে, কখনো বাসের ছাদে বসে! নিচু হয়ে থাকা গাছের ডালে ছাদে বসে থাকা প্যাসেঞ্জারদের যেন ধাক্কা খেতে না হয়, তার দায়িত্ব নিয়েছিল সদ্য যুদ্ধ থেকে ফেরা একজন বাচ্চা মুক্তিযোদ্ধা-দূর থেকে একটা নিচু গাছের ডাল দেখলেই সে চিৎকার করে উঠত, ‘এমবুশ!’ এবং আমরা ছাদে বসে থাকা সবাই এমবুশ করতাম-অর্থাৎ মাথা নিচু করে ফেলতাম! যখন বয়স কম থাকে তখন কিভাবে কিভাবে জানি নিজের ভেতরে একটা নিশ্চিত ধারণা হয়ে যায়, ‘আমার কিছু হবে না!’ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, একজন দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে যেহেতু এ ধরনের অসংখ্য পাগলামো করেছি, আমার মতো অন্যরা কেন করবে না? তাই ঈদের আগে যখন দেখি ট্রেনের ছাদে বসে অসংখ্য মানুষ, মহিলা, শিশু, পরিবার বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাড়ি যাচ্ছে; আমি তাদের দোষ দিতে পারি না। শুধু মনে মনে খোদার কাছে দোয়া করে বলি, খোদা সবাইকে সুস্থ দেহে বাড়ি পৌঁছে দাও। অপেক্ষা করি, একদিন বাংলাদেশ আরেকটু সচ্ছল একটা দেশ হবে; তখন কাউকে বাস কিংবা ট্রেনের ছাদে করে বাড়ি যেতে হবে না। রাষ্ট্র আইন করে এটা বন্ধ করে দিতে পারবে।
এ দেশের পথেঘাটে যারা চলাফেরা করেছে, তাদের সবারই ছোট-বড় কোনো না কোনো দুর্ঘটনার কবলে পড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমারও হয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে সিলেট থেকে গণিত অলিম্পিয়াডে যোগ দেওয়ার জন্য কুমিল্লা যাচ্ছি। প্রচণ্ড কুয়াশায় একটা ভাড়া করা মাইক্রোবাসে আমরা কয়েকজন বসে আছি। কুয়াশার কারণে যেহেতু পথঘাট দেখা যাচ্ছে না, আমি পুরোপুরি সজাগ থেকে ড্রাইভারের গতিবিধি দেখছি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই-গাড়ির ড্রাইভার প্রচণ্ড রেগে তার গাড়ি দিয়ে সামনে একটা ট্রাককে মেরে বসল। মনে হলো, বিকট শব্দে গাড়িটি টুকরো টুকরো হয়ে গেল, ভেতরে সবাই আমরা সামনে ছিটকে পড়েছি; আমার পাশে বসা আমাদের একজন সহকর্মী তাঁর সিট থেকে প্রায় উড়ে গিয়ে সামনের উইন্ড শিল্ডে গিয়ে আঘাত করলেন; আমি দেখলাম, মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন, মাথা থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। মাইক্রোবাসের দরজা খুলে সবাই কোনোমতে বের হয়েছে, যে সহকর্মী মাথায় আঘাত পেয়েছেন, তাঁর অবস্থা খুব খারাপ; অন্য সবাই কমবেশি পেলেও কারো আঘাত গুরুতর নয়। আমরা মাথায় আঘাত পাওয়া সহকর্মীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। অ্যাক্সিডেন্টে হাত-পা ভাঙা এক ব্যাপার, মাথায় আঘাত পাওয়া সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। আহত সহকর্মীকে এই মুহূর্তে হাসপাতালে নেওয়া দরকার। ভোরবেলা কুয়াশা ঢাকা পথের পাশে একটা দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি, পথের পাশে মাথায় আঘাত নিয়ে একজন রক্তাক্ত আহত যাত্রী শুয়ে আছেন। আমি দেখলাম, রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গতি কমিয়ে বিষয়টা কৌতূহল নিয়ে দেখছে; কিন্তু সাহায্য করার জন্য কেউ থামছে না। একটা দামি কালো পাজেরো পাশ দিয়ে চলে গেল, গতি কমিয়ে আমাদের সবাইকে একনজর দেখে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।
কী করব বুঝতে না পেরে আমি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামানোর চেষ্টা করছি। শেষ পর্যন্ত একটা ট্রাক থামাতে পারলাম। ট্রাকের ড্রাইভার আমাদের আহত সহকর্মীকে কাছাকাছি হাসপাতালে পৌঁছে দিতে রাজি হলো। আমরা কোনোমতে তাঁকে ট্রাক ড্রাইভারের পাশের সিটে বসিয়ে কাছাকাছি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলাম। সেখানে এই কাকভোরেও একজন ডাক্তার আছেন। রোগী পরীক্ষার বিছানায় একজন শুয়ে আছেন। কাছে গিয়ে দেখা গেল, সেটি একজনের মৃতদেহ। তাঁকে ধরাধরি করে নিচে নামিয়ে আমাদের সহকর্মীকে সেখানে শোয়ানো হলো, ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে আমাদের আশ্বস্ত করলেন। ততক্ষণে চারদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে, দেখতে দেখতে অনেকে এগিয়ে এলো সাহায্যের জন্য। তবে যে বিষয়টি আমি কখনো ভুলিনি, প্রয়োজনে সবার আগে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে একজন ট্রাক ড্রাইভার এবং তার হেলপার। আমি সেই ট্রাক ড্রাইভারের নম্বর নিয়ে রেখেছিলাম, ইচ্ছা ছিল সব কিছু ঠিকঠাক হওয়ার পর তার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি ভালোভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব। আমার অগোছালো স্বভাবের কারণে টেলিফোন নম্বরটি হারিয়ে ফেলেছি বলে আর কখনো তাকে ঠিক করে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারিনি।
আমি অনেকবার লক্ষ করেছি, বড় ধরনের বিপদের সময় খুব সাধারণ মানুষরা সাহায্যের জন্য সবার আগে এগিয়ে আসে। একবার ডিপার্টমেন্টে কাজ করছি, তখন হঠাৎ কিছুদিন আগেও আমার ছাত্র ছিল, সে রকম একজন সহকর্মীর ফোন এসেছে। ফোন ধরতেই শুনি, সে হাউমাউ করে কাঁদছে, একটু শান্ত হয়ে বলল, সে দুটি বাসের একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষের ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছে (সেই অ্যাক্সিডেন্টে ১৬ জন মারা গিয়েছিল)। এই মুহূর্তে হাসপাতালের অসংখ্য আহত যাত্রীর মাঝে পড়ে আছে। তার সঠিক চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করে কোনোভাবে ঢাকায় ভালো হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার কাছে শুনেছিলাম, অ্যাক্সিডেন্টের পর জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আবিষ্কার করল, একজন রিকশাওয়ালা তাকে জানালা দিয়ে টেনে কোনোভাবে বের করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। তার হাতে তার ব্যাগটাও ধরিয়ে দিয়েছে। তারপর ছুটে গেছে অন্য আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সে কারো জন্য অপেক্ষা না করে নিজ দায়িত্বে একের পর এক আহত যাত্রীদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। আমি ঠিক করেছিলাম, সুস্থ হওয়ার পর আমার সেই ছাত্রকে নিয়ে আমরা সেই ছোট শহরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে সেই রিকশাওয়ালাকে বের করে তার হাত ধরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসব। নানা কাজে ব্যস্ত থাকার অজুহাতে সেই কাজটিও করা হয়নি, যদি সত্যি করতে পারতাম; সেটি কী সুন্দর একটা গল্প হতে পারত।
ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা
২.
দেশে কিভাবে রাস্তাঘাট ঠিক করা যায় কিংবা কিভাবে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আমি মোটেও তার এক্সপার্ট নই। কিন্তু যেহেতু আমাকে এই দেশের রাস্তাঘাটে অসংখ্যবার যেতে-আসতে হয়েছে, অসংখ্য বিষয় দেখতে হয়েছে; তাই নিজের অভিজ্ঞতাটুকু একটু লিখছি।
আমার কাছে কোনো পরিসংখ্যান নেই; কিন্তু তার পরও আমার ধারণা, বাংলাদেশে গাড়ি দুর্ঘটনায় যত মানুষ মারা যায়, তার একটা বড় অংশ হচ্ছে পথচারী। বড় হাইওয়ে অনেক জায়গায় প্রায় মানুষের বাড়ির উঠানের ওপর দিয়ে চলে গেছে, ছোট বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে, বাড়ির মেয়েরা কলসি দিয়ে পানি আনছে, ছেলেরা গরু নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সবার গা ঘেঁষে অতিকায় বাস-ট্রাক এক শ-দেড় শ কিলোমিটার বেগে হুশ করে ছুটে যাচ্ছে। এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে দেখতে হয়, বড় বড় বাস-ট্রাকের ভেতর দিয়ে ছোট একটা শিশু হাইওয়ে পাড়ি দিয়ে যাচ্ছে এবং খুব কাছেই তাদের মা-বাবা গল্প করছেন। খোলা জায়গার অভাব, তাই ধান শুকানোর জন্য হাইওয়ে ব্যবহার করাকে কষ্ট করে মেনে নিতে রাজি আছি; কিন্তু বাস-ট্রাকের তোয়াক্কা না করে সেই ধান পা দিয়ে মাড়াই করার দৃশ্য খুবই ভয়ংকর। যে বিষয়টি আমার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় সেটি হচ্ছে, যখন একজন মানুষ মোবাইল টেলিফোনে কথা বলতে বলতে কোনো দিকে না তাকিয়ে হাইওয়ের এক পাশ থেকে অন্য পাশে পার হয়ে যায়। তাদের হাঁটার ভঙ্গিতে সব সময়ই এক ধরনের শৌর্যবীর্য এবং অহংকার থাকে। গাড়ি বা বাস-ট্রাককে তাদের সমীহ করে কোনোভাবে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। আমি নিশ্চিত, সব সময় সেটি সম্ভব হয় না এবং সম্পূর্ণ বিনা কারণে এ রকম অসংখ্য দুঃসাহসী পথচারী মারা পড়ে। আমার মনে হয়, সাধারণ পথচারীদের জোর করে হলেও বোঝানো উচিত যে একটা চলন্ত বাস-ট্রাক বা গাড়ি মোটেও তাচ্ছিল্য করার কিছু নয়। স্কুলে বাচ্চাদের বইয়ে পথঘাটে কেমন করে চলা উচিত, তার ওপর কোনো পাঠ্যসূচি আছে কি না জানি না। যদি না থাকে, সেটি মনে হয়, চমৎকার একটা পাঠ্যসূচি হতে পারে।
তবে এটি প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আমাদের দেশের দুর্ঘটনার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, বেপরোয়া ড্রাইভার। ট্রাকগুলোতে যে পরিমাণ মালপত্র বোঝাই করা সম্ভব, সব সময়ই তার থেকে অনেক বেশি বোঝাই করা হয় বলে তারা সেভাবে ছোটাছুটি করতে পারে না, অনেকটা ধীরগতিতে রাস্তা দখল করে যেতে থাকে; কিন্তু বাস ড্রাইভাররা হচ্ছে সবচেয়ে বেপরোয়া। তাদের ড্রাইভিং দেখে আমার সব সময়ই মনে হয়, এই ড্রাইভারদের শৈশবের স্বপ্ন ছিল প্লেনের পাইলট হওয়ার; কিন্তু তা না হয়ে তাদের হতে হয়েছে বাসের ড্রাইভার। কিন্তু শৈশবের স্বপ্নটা কখনো ভুলতে পারেনি, তাই প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করে বাসটিকেই কোনোভাবে উড়িয়ে নিয়ে যেতে! একটা সেকেন্ড সময় বাঁচানোর জন্য তারা নিজেদের এবং অন্যদের জীবনের ওপর যে পরিমাণ ঝুঁকি নেয়, সেটা বিশ্বাস করা কঠিন। যাঁরা বাংলাদেশের হাইওয়েতে যাতায়াত করেছেন তাঁরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন, আমাদের দেশের গাড়ি ওভারটেক করার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর। সারা পৃথিবীতে একটা নিয়ম মেনে চলা হয়, সেটি হচ্ছে রাস্তার এক পাশ দিয়ে গাড়ি যাবে, অন্য পাশ দিয়ে বিপরীত দিকের গাড়ি আসবে। আমাদের দেশের অলিখিত নিয়ম হচ্ছে, যে গাড়ি সাইজে বড় সে রাস্তার যেকোনো দিক দিয়ে যাবে কিংবা আসবে, কেউ তাকে কিছু বলতে পারবে না! অর্থাৎ যে গাড়ি সাইজে যত বড় রাস্তায় তার তত বেশি অধিকার। বিপরীত দিক থেকে গাড়ি এলে পৃথিবীর কোথাও ওভারটেক করে না, আমাদের দেশে সেটি নিয়মিতভাবে করা হয়। বিপরীত দিকের গাড়িটির সাইজ যদি ছোট হয়, তাহলে বড় গাড়িটির জন্য তাকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়; রাস্তা থেকে পাশের খানাখন্দেও নেমে যেতে হয়!
এ ধরনের অচিন্তনীয় বিপজ্জনক ওভারটেক সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপের কারণে বেশির ভাগ সময়ই কাজ করে, মাঝেমধ্যে কাজ করে না এবং তখন আমরা জানতে পারি, দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। ১০, ২০ কিংবা ৩০ জন অসহায় প্যাসেঞ্জার সম্পূর্ণ বিনা কারণে মারা গেছে। এর জন্য কারো কোনো দায়দায়িত্ব নেই। আমরা শুধু মৃত্যুর সংখ্যাটি পত্রপত্রিকায় দেখি; কিন্তু যারা সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে, চিকিৎসার খরচ দিতে গিয়ে পুরো পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে, সংসারে উপার্জনের কোনো মানুষ নেই বলে পুরো পরিবারটি পথে বসেছে, তার খোঁজ কখনো পাই না।
এখন আমাদের বেশির ভাগ হাইওয়ে এক রাস্তার হাইওয়ে। দেশের অর্থনীতি যত ভালো হবে এই রাস্তাগুলোর তত উন্নতি হবে। মাঝখানে ডিভাইডার দিয়ে দুই রাস্তার হাইওয়ে হবে এবং এই ভয়ংকর ওভারটেকগুলোর বিপদ কমে আসবে। কিন্তু যত দিন সেটি না হচ্ছে তত দিন আমাদের এই রাস্তা এবং এই ড্রাইভারদের নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। কেন জানি আমার মনে হয়, আমরা কখনো আমাদের ড্রাইভারদের নিরাপদে গাড়ি চালানোর বিষয়টি শেখানোর চেষ্টা করিনি। মনে আছে, একবার আমি একটা বাসের ড্রাইভারকে খুবই বিনয়ের সঙ্গে আস্তে গাড়ি চালাতে অনুরোধ করছিলাম। বাসের ড্রাইভার একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘স্যার, আপনি একমাত্র মানুষ, যে আমাকে আস্তে গাড়ি চালাতে বলেছেন! অন্য সব প্যাসেঞ্জার আমি যত জোরে গাড়ি চালাই তারা তত খুশি!’ ড্রাইভারের বক্তব্য কতটুকু সত্যি, কতটুকু অতিরঞ্জিত আমি কখনো যাচাই করে দেখতে পারিনি।
বেশ কয়েক বছর আগে একটা বড় অ্যাক্সিডেন্টে অনেক মানুষ মারা যাওয়ার পর আমি ড্রাইভার, ড্রাইভিং, ড্রাইভিং টেস্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স-এই বিষয়গুলোর খোঁজখবর নিয়েছিলাম। তখন আমি একটা বিচিত্র বিষয় আবিষ্কার করেছিলাম, ড্রাইভিং লাইসেন্স নেওয়ার জন্য যে লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়, সেই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সরকার থেকে প্রকাশিত কোনো বই নেই। ব্যক্তিগতভাবে লেখা একটা বই রয়েছে এবং সেই বইয়ে ড্রাইভিংয়ের নিয়মকানুনের সঙ্গে গাড়ির কলকবজা এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে অনেক তথ্য আছে। বইটি পড়ে আমার মনে হয়েছিল, আমাদের ড্রাইভিং টেস্ট নিশ্চয়ই একই সঙ্গে গাড়ির ড্রাইভার এবং গাড়ির মেকানিক হওয়ার টেস্ট! শুধু তা-ই নয়, বইয়ের উপস্থাপনা যথেষ্ট জটিল। এই দেশের অল্প শিক্ষিত মানুষের জন্য সেই বই পড়ে ড্রাইভিং টেস্টে পাস করা মোটেও সহজ নয়।
পৃথিবীর সব দেশেই এই বিষয়গুলো সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। খুব সহজ ভাষায়, সুন্দর করে ড্রাইভিং টেস্ট নেওয়ার জন্য ছোট চটি বই থাকে। যারা ড্রাইভিং শিখতে চায় তাদের সবাইকে প্রথমে এই ছোট চটি বই পড়ে একটা লিখিত পরীক্ষায় পাস করতে হয়। আমেরিকায় গাড়ি চালানো শেখার আগে আমাকেও এই বই পড়ে একটা লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। বইটি উল্টেপাল্টে দেখে আমি লিখিত পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং পরীক্ষা শেষে আমাকে জানানো হলো, আমি পরীক্ষায় ফেল করেছি। আমার জীবনে সেটি প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র পরীক্ষা ফেল-তখন টের পেয়েছিলাম, পরীক্ষায় ফেল করলে খুবই অপমান বোধ হয়। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে আমি সেই বইটি শুধু উল্টেপাল্টে না দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছিলাম!
আমার ধারণা, যেহেতু আমাদের ড্রাইভারদের বেশির ভাগই ড্রাইভিংয়ের অত্যন্ত মৌলিক কিছু বিষয় কখনোই শেখে না, তারা শুধু গাড়িটিকে চালাতে শেখে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। তাই তারা অহেতুক নিজেকে এবং প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে ভয়ংকর ঝুঁকিগুলো নিয়ে থাকে। তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হলে অনেকে নিশ্চয়ই নিরাপদে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করবে।
আমি সারা জীবন মানুষের ভেতরকার শুভবোধকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। যখন কোনো নিষ্ঠুর অ্যাক্সিডেন্টে সম্পূর্ণ অকারণে অনেক মানুষ মারা যায়, আমরা সব সময়ই তার জন্য দোষী মানুষটাকে খুঁজে বের করে তার একটা শাস্তি দিয়ে বিষয়টুকু শেষ করতে চাই। বেশির ভাগ সময়ই ড্রাইভার হচ্ছে সেই দোষী মানুষ; কিন্তু গাড়ির মালিক এই ড্রাইভারকে ঘুমানোর সুযোগ দিয়েছেন কি না, তাকে নিরাপদে গাড়ি চালানোর পরিবেশটুকু তৈরি করে দিয়েছেন কি না তার খোঁজ নিই না। আমি নিজে যেহেতু দীর্ঘদিন গাড়ি চালিয়েছি, তাই আমি জানি দুই ঘণ্টা টানা গাড়ি চালানোর পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া কত জরুরি। আমরা কি আমাদের দেশে ড্রাইভারদের কখনো সেই বিশ্রামটুকু দিই? ধরেই নিই, একজন গাড়ির ড্রাইভার আসলে গাড়িটির মতোই একটা মেশিন!
আমাদের দেশের পথে অকারণে এত মানুষ মারা যায়, তাদের জন্য এই পুরো ব্যাপারটা কি আরো অনেক গুরুত্ব নিয়ে আমাদের দেখা উচিত না? আরো একটু বাস্তব চোখে? আরো একটু সহমর্মিতা নিয়ে? অসহায় মানুষদের আর কত দিন এভাবে মারা যেতে দেব?
লেখক : অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট


 Reporter Name
Reporter Name