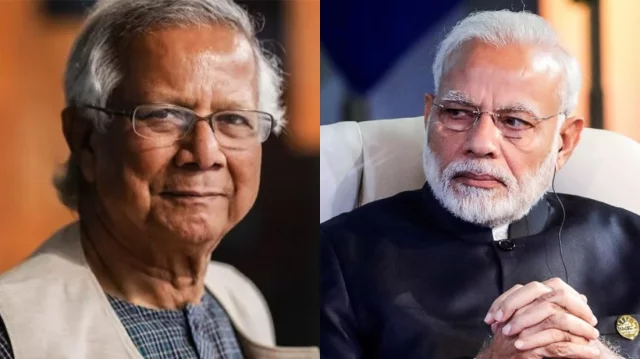ফজলুল হক এক বিচিত্র মানুষ। খেয়ালের বশে তিনি অনেক কিছু করতেন। খুব স্বপ্নবান পুরুষ। নতুন কিছু করার ব্যাপারে তার অনেক আগ্রহ। এ দেশে তিনিই প্রথম ছোটদের চলচ্চিত্র ‘সান অব পাকিস্তান’ নির্মাণ করেন। হাউজিং ব্যবসার সূত্রপাত করেন। তিনি প্রথম বাংলা ডায়াল ঘড়ির প্রচলন করেন। রেস্টুরেন্টে খিচুড়ি আর হাঁসের মাংসের মেন্যু চালু করেন। সবচেয়ে বড় সাফল্য তিনিই প্রথম চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা ‘সিনেমা’র (পঞ্চাশ দশকে প্রকাশিত) সম্পাদক ছিলেন।
সময়কাল ১৯৬৮। তখন তার চলচ্চিত্রের অফিস ছিল ঢাকার ৯১ নওয়াবপুর রোডে। সম্পর্কে তিনি আমার পিতা। আমি তার জ্যেষ্ঠ সন্তান। একদিন তিনি বেবিট্যাক্সি করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরেছেন। সারাদিন অফিসে অনেক কাজ করেছেন। ক্লান্ত দেহমন। বেবিট্যাক্সিটা কিছুদূর গিয়ে গরগর শব্দ করে থেমে গেল। বেবিট্যাক্সি নামের সেই বাহনটি এখন আর দেখা যায় না। বেবিট্যাক্সি যানবাহনটি আজকের দিনের সিএনজিচালিত বাহনের মতো। তখন বেবিট্যাক্সি চেপে ঢাকার বাইরে যাওয়া যেত।
বাবা চুপ হয়ে বসেছিলেন। গাড়ি নষ্ট হওয়ায় বাবার ধ্যান ভাঙল। তিনি কিছুটা বিরক্ত। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে আবার কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল। বাবা মহাবিরক্ত। গাড়ি বন্ধ হচ্ছে আবার চালু হচ্ছে।
তখন বাবা ড্রাইভারকে বললেন, তুমি কি গাড়ি চালাও নাকি অন্যকিছু করো?
লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, স্যার আমি দিনের বেলা পিঠা বানাই।
মানে!
পিঠা বানাই। সেই পিঠা লোকজন কিনে নিয়ে যায়।
কোথায় বানাও?
কেরানীগঞ্জে। সেখান থেকে ঢাকায় পিঠা আসে।
বাবা খুব মজা পেলেন।
তুমি কাল আমার অফিসে আসতে পারবে?
পারব স্যার?
তখন ঢাকা শহরে গলি বা রাস্তার ধারে পিঠাওয়ালী ছিল না। পিঠার প্রচলন ছিল গ্রামগঞ্জে। বাবা অভিনব আইডিয়া করলেন। পিঠা খাওয়াবেন বাঙালিদের। আমার বড় চাচিÑ ড. ফজলুল করীমের সহধর্মিণী। তিনি রান্না করে সবাইকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। বাবা তার সঙ্গে আলোচনা করলেন। আমার মা প্রখ্যাত লেখক রাবেয়া খাতুন সব শুনে ক্ষেপে গেলেন। বাবার চিন্তা পাগলামি মনে করলেন।
বাবা বললেন, তুমি খিচুড়ি রান্না করে দেবে। আর হাঁসের মাংস। আশা করি বিক্রি ভালোই হবে। চাচি রেঁধে পাঠালেনÑশিঙাড়া, সমুচা, এসব। জায়গা খোঁজা শুরু হলো। পল্টনে চলচ্চিত্র পরিচালক ইবনে মিজানের বাড়ির উল্টোদিকে খালি ঘর পাওয়া গেল। আশপাশে ডোবানালা। কোনো হোটেল-রেস্টুরেন্ট নেই। দোকানের নাম দেওয়া হয় ‘পিঠাঘর’ আর পিঠাঘরের স্লোগান ছিল ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।’ ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় প্রতিষ্ঠিত হলো পিঠার দোকান। কবি শামসুর রাহমান এই পিঠাঘরের উদ্বোধন করেন।
দোকান কী করে চলবে এসব নিয়ে বাবার কোনো ভাবান্তর নেই। ১৯৬৯ থেকে ‘আমি কে তুমি কে, বাঙালি বাঙালি।’ এই স্লোগান তখন সবখানে। নাগরিক জীবনে পিঠা তখন অদ্ভুত আবেশ নিয়ে এলো। খুব স্বল্প সময়ে খুব জনপ্রিয় হলো ‘পিঠাঘর’।
মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সেই প্রথম পিঠার প্রচলন শুরু হলো। বাংলার খাবার নাগরিক জীবনে নতুন ধারা তৈরি করল। যিনি বাবার কাছে প্রথম পিঠাপুলির কথা উচ্চারণ করেছিলেন সেই বেবিট্যাক্সিচালকের নাম ছিল ধনু মিয়া। তিনিই পরে বিখ্যাত পিঠা বানানোর কারিগর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
দুই
বাঙালি খাদ্যরসিক জাতি। বাঙালির খাদ্য ঐতিহ্যের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ ঐতিহ্য। ডাল-ভাত ছাড়া বাঙালি কিন্তু ‘মাছে-ভাতে’ বাঙালি হিসেবে পরিচিত। পিঠা বাঙালির আরেক ঐতিহ্য। শীতের শুরুতে বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠার উৎসব। কত রকমের পিঠা যে বাঙালি রমণীরা বানাতে জানে তার কোনো হিসাব নেই। অঘ্রাণে নতুন ধান ওঠে। নতুন ধানের সুবাসে ম-ম করে বাংলার মাঠ প্রান্তর। বাংলার মায়েরা তখন নতুন ধানের ঢেঁকিছাঁটা চালের গুঁড়ো দিয়ে পিঠা তৈরি করে। পিঠা যেন বাংলার ঘরে নতুন স্বপ্ন নিয়ে আসে। জীবনের সঙ্গে মিশে থাকে পিঠার ঘ্রাণ। পিঠা যেন সামাজিক উৎসবের প্রতীক। বিবাহ, জামাইয়ের আগমন, প্রতিবেশীদের পিঠার আমন্ত্রণ জানানোÑ এ রকম নানা অনুষ্ঠানে পিঠার ব্যবহার দেখা যায়। কোনো কোনো জেলায় পিঠা পাঠিয়ে যে কোনো আমন্ত্রণ জানানোর রীতিও আছে। আত্মীয়স্বজন বেড়াতে এলে তাকে পিঠা দিয়ে বরণ করা হয়। আপ্যায়নের প্রধান অনুষদ পিঠা। এই সেদিনও নিমন্ত্রণ দেওয়ার সময় এক থালা পিঠা পাঠানো হতো বাড়ি বাড়ি।
আমাদের সমাজে পিঠার বিচিত্র সম্ভার। নারকেল দুধ, খেঁজুর গুড়, চালের গুঁড়া ব্যবহার করে শত শত রকমের পিঠা তৈরি করা হয়। কত রকমের যে পিঠা, নাম বলে শেষ করা যাবে না। নকশি পিঠা, পাটিসাপটা, তেলের পিঠা, পাকন পিঠা, ভাপা পিঠা, ফুল, চিতই, চাপটি, পানতোয়া, ঝালপোয়া, পুলি, ক্ষীরপুলি, মালাই পিঠা, দুধ চিতই, মালাই, মেরা পিঠা, সন্দেশ, সেমাই পিঠা, চুই পিঠা, তালের পিঠা, ঝিঁনুক পিঠা, ইলিশ পিঠা, নারকেল পিঠা, কলা পিঠাসহ কত রকমের পিঠা যে তৈরি হয় বাংলার ঘরে ঘরে।
আমার বাবা ফজলুল হক ষাট দশকের শেষে সেই সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলার ঘরে ঘরে তিনি পিঠাকে ‘অভিজাত’ খাবার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। আজ সর্বত্র যখন যথেষ্ট পরিমাণে পিঠার ব্যবহার দেখি নাগরিকদের মধ্যে তখন স্মরণে আসে ফজলুল হকের কথা। তার অবদান আমরা কী করে ভুলব!
তিন
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ উঠিয়ে দেওয়া হয়। ভেঙে দেওয়া হয় পিঠাঘরের যন্ত্রপাতি। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হলো বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠার একটি দোকান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে অশ্রুসজল চোখে বাবা তাকিয়ে দেখেছেন জীর্ণ দোকানের শীর্ণ অবয়ব।
পরে বাবা ‘সোনার চামচ’ নামে একটি দোকান আবার চালু করেন। পরে ’৮০-র দশকে চালু হয় খাবার দাবার পিঠাঘর। সে আরেক কাহিনি। অন্যত্র বলা যাবে।
ফরিদুর রেজা সাগর : শিশুসাহিত্যিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব


 Reporter Name
Reporter Name