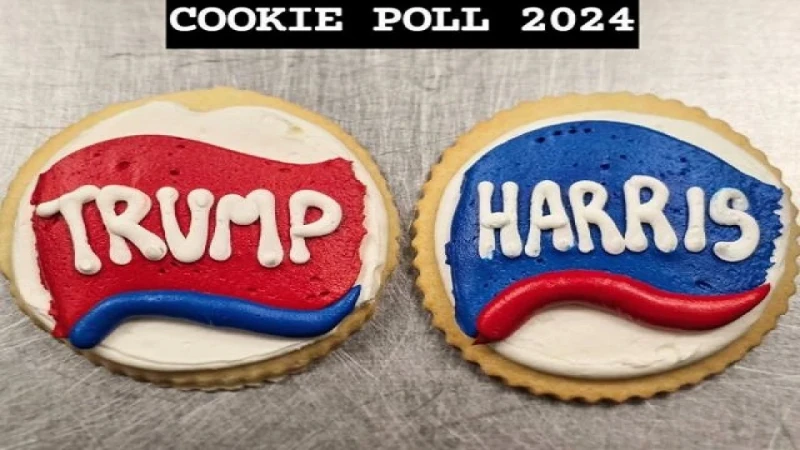হাওর বার্তা ডেস্কঃ দেশে ১৯৮৮ সালের পর আবার একটা বড় বন্যা হয়েছে। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফসলের। ভেঙে গেছে অসংখ্য বসতবাটি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেতু, সড়ক- মহাসড়ক, রেলপথ। ভেসে গেছে বিপুলসংখ্যক গবাদিপশু, হাঁস মুরগি, দৈনন্দিন বেঁচে থাকার উপাদান। টেলিভিশনের খবরে দেখলাম মায়ের হাত থেকে ছুটে গেছে সাত বছরের এক শিশু। ২৩ আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে বন্যায় মারা গেছেন ১২১। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিতভাবেই কয়েক হাজার কোটি টাকা হবে। জীবন বাঁচাতে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে অবস্থান নিয়েছিলেন ৬৭ লাখ মানুষ। পানি নেমে যাওয়ার পর তাদের অনেককে শূন্য থেকে নতুন জীবন শুরু করতে হয়েছে। এ চিত্রটা নতুন নয়। আমাদের জানা ইতিহাস জুড়েই বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস ও সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এ ভূখণ্ডের মানুষদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। সংঘটিত বন্যার ওপর অধ্যাপক পিসি মহলানবিশ এক গবেষণায় দেখিয়েছেন বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ১৮৭০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত মাঝারি আকারের বন্যা গড়ে প্রতি দুই বছরে একবার এবং ভয়াবহ বন্যা গড়ে ৬-৭ বছরে একবার সংঘটিত হয়েছে। আর প্রতি শতাব্দীতে ছয়টি করে মহাপ্লাবনের মুখোমুখি হয়েছে এই বঙ্গীয় বদ্বীপ যার একটা আমরা দেখেছি ১৯৮৮ সালে।
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (৩২১-২৯৬ খ্রিষ্টপূর্ব) শাসনামলে তাঁর অর্থমন্ত্রী কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রতি দশকে গড়ে একবার অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, ভয়াবহ বন্যায় ব্যাপক প্রাণহানি, ফসল বিনষ্ট ও গবাদিপশুর মৃত্যুর কথা উল্লেখ আছে। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বন্যাটা হয়েছে চীনে ১৯৩১ সালে যাতে ২৪ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিল। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছিল ১৮৭৬ সালে যাতে মারা যায় দুই লাখ পনেরো হাজার মানুষ। সে সময় পানির উচ্চতার রেকর্ডটি পাওয়া যায় না। সংরক্ষিত রেকর্ড অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি উচ্চতার পানি প্রবাহ ঘটেছে ১৯৫২ সালে। সে বছর ১ আগস্ট সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানির উচ্চতা ছিল ১৪.২২ মিটার এবং ৩০ আগস্ট হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে পদ্মা নদীর পানির উচ্চতা ছিল ১৪.৯১ মিটার। হার্ডিঞ্জ ব্রিজে ১৯৮৮ সালে এটা ছিল ১২.৮০ মিটার। এ অঞ্চলে নিকট অতীতের বন্যায় প্রাণহানির পরিসংখ্যানটা মোটামুটি এরকম চীনে ১৯৮৯ ও ১৯৯৮ সালে মারা গেছে যথাক্রমে তিন হাজার ৮০০ ও তিন হাজার ৬০০ মানুষ। নেপালে ২০০২ সালে মারা গেছে সাড়ে ৪৫০ জন। ভারতের বিহারে বন্যায় ১৯৮৭ সালে এক হাজার ৪০০ জন মহারাষ্ট্রে ২০০৫ সালে এক হাজার ১০০ জন, উত্তরাখন্ডে ২০১৩ সালে পাঁচ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।
মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। আমরা বুঝতে চেষ্টা করি বাংলাদেশে বন্যার মূল কারণ কি এবং বন্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরা, শিলং মালভূমির পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর বরাবর বিস্তৃত অঞ্চলে এই বদ্বীপের অবস্থান। মূলত হিমালয়ের উচ্চভূমি থেকে আগত নদীধারা কর্তৃক বাহিত পলিমাটি দ্বারা বঙ্গীয় বদ্বীপের সৃষ্টি। ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীনের অংশবিশেষের প্রধান নদীগুলো বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কারণ এটাই এই এলাকার সবচেয়ে নিচু অঞ্চল।
বাংলাদেশের প্রধান তিন নদীর গতিপথ
প্রতিবছর গড়ে বাংলাদেশের তিনটি প্রধান নদীপথে মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আর্দ্র মৌসুমে ৮ লাখ ৪৪ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি প্রবাহিত হয়। একই সময় দেশের অভ্যন্তরে ১ লাখ ৮৭ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার নদী প্রবাহ সৃষ্টি হয় বৃষ্টিজনিত কারণে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সম্মিলিত পানির প্রবাহ লোয়ার মেঘনা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। কোনো বছর চীন,ভারত, ভুটান ও নেপালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে তা এ অঞ্চলের নদীগুলোর নির্গমন ক্ষমতাকে ছাপিয়ে যায়। ফলে পুরা অঞ্চলটিতেই বন্যা দেখা দেয়। এ বছরও একই ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও নেপালে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং বন্যা হয়েছে। এই দেশগুলিতে মারা গেছে যথাক্রমে ১২১, ২৫৩, ৫৭ ও ১৪৫ জন মানুষ।
বন্যার কারণ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটা ভুল ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে। বলা হয় উজানের দেশগুলিতে বাঁধ খুলে দিয়ে আমাদের দেশে কৃত্রিম উপায়ে বন্যা ঘটানো হয়। সবচেয়ে বেশি বলা হয় ফারাক্কা বাঁধের কথা। বন্যার পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে আমরা দেখব এ অঞ্চলে বিগত দুই শ বছরে গঙ্গা অববাহিকায় সংঘটিত সাতটি প্রলয়ংকরী বন্যার একটি ঘটেছে ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার পর (১৯৮৮ সালে)। বাকি বন্যাগুলো সংঘটিত হওয়ার সময় ফারাক্কা বা অন্য কোনো ক্রস ড্যাম ছিল না। রেকর্ড অনুযায়ী গঙ্গা নদীর সর্বোচ্চ অন বেড পানিপ্রবাহ ৭৫ হাজার কিউসেক। অর্থাৎ এই পরিমাণ পানি গঙ্গা দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে কুল না ছাপিয়ে। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পর এর মধ্যে ১১ হাজার কিউসেক পানি হুগলি নদীতে প্রবাহিত করা হয়। বাকি ৬৪ হাজার কিউসেক ফারাক্কা পয়েন্টে পৌঁছালে তা পদ্মায় প্রবাহিত করা সম্ভব। কারণ ফারাক্কা ব্যারেজের সর্বোচ্চ নির্গমন ক্ষমতা ৬৫ হাজার কিউসেক।
 ছবি: পান্না বালাভরা বর্ষায় ফারাক্কার সবগুলো গেট খুলে রাখলে বাংলাদেশে মাঝারি বা নিম্ন মাঝারি মাত্রার (অন্য নদীগুলোর প্রবাহের ওপর ভিত্তি করে) বন্যা হবে। গঙ্গার সর্বোচ্চ পানি প্রবাহের সঙ্গে যখন অতিবৃষ্টির পানি যোগ হয় তখন সেটা কুল ছাপিয়ে পশ্চিম বাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে ফেলে এবং সমতলভূমির ওপর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এ বছর সেটা ঘটেছে ব্রহ্মপুত্রের ক্ষেত্রে। স্যাটেলাইট থেকে নেওয়া বন্যার চিত্র দেখলে বিষয়টা স্পষ্ট বোঝা যায়। নাসার আর্থ অবজারভেটরি পেজে সম্প্রতি এই স্যাটেলাইট ইমেজটি আপলোড করা হয়েছে। এখানে বন্যায় নিমজ্জিত অংশকে হালকা সবুজ (ফিরোজা) রঙে দেখা যাচ্ছে। নীল রঙে চিত্রিত ব্রহ্মপুত্র নদকে দেখা যাচ্ছে ৫০ থেকে ১০০ কিলোমিটার প্রশস্ত। যেখানে তার প্রকৃত প্রস্থ ৮ থেকে ১৮ কিলোমিটার। দিনাজপুর থেকে নিচের দিকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত প্লাবিত এলাকাকে সাদা দেখা যাচ্ছে সূর্যের আলোর প্রতিফলনের কারণে।
ছবি: পান্না বালাভরা বর্ষায় ফারাক্কার সবগুলো গেট খুলে রাখলে বাংলাদেশে মাঝারি বা নিম্ন মাঝারি মাত্রার (অন্য নদীগুলোর প্রবাহের ওপর ভিত্তি করে) বন্যা হবে। গঙ্গার সর্বোচ্চ পানি প্রবাহের সঙ্গে যখন অতিবৃষ্টির পানি যোগ হয় তখন সেটা কুল ছাপিয়ে পশ্চিম বাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে ফেলে এবং সমতলভূমির ওপর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এ বছর সেটা ঘটেছে ব্রহ্মপুত্রের ক্ষেত্রে। স্যাটেলাইট থেকে নেওয়া বন্যার চিত্র দেখলে বিষয়টা স্পষ্ট বোঝা যায়। নাসার আর্থ অবজারভেটরি পেজে সম্প্রতি এই স্যাটেলাইট ইমেজটি আপলোড করা হয়েছে। এখানে বন্যায় নিমজ্জিত অংশকে হালকা সবুজ (ফিরোজা) রঙে দেখা যাচ্ছে। নীল রঙে চিত্রিত ব্রহ্মপুত্র নদকে দেখা যাচ্ছে ৫০ থেকে ১০০ কিলোমিটার প্রশস্ত। যেখানে তার প্রকৃত প্রস্থ ৮ থেকে ১৮ কিলোমিটার। দিনাজপুর থেকে নিচের দিকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত প্লাবিত এলাকাকে সাদা দেখা যাচ্ছে সূর্যের আলোর প্রতিফলনের কারণে।
বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় বের করার জন্য সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। তবে তাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। ১৯৮৬ সালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সারফেস ওয়াটার সিমুলেশন মডেলিং প্রোগ্রাম (SWSMP) চালু করা হয়। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পরে বাংলাদেশ সরকার বন্যার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের জন্য ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (FAP) গ্রহণ করে। ইউএসএআইডির কারিগরি সহায়তা এবং নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক সহায়তায় সম্পাদিত পরিবেশগত সমীক্ষা (FAP ১৬) ও ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (GIS) সমীক্ষার (FAP ১৯) মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পানি খাতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করা হয়। সেখানে বন্যা সংঘটনের জন্য দায়ী হিসেবে যে কারণগুলো চিহ্নিত করা হয় সেগুলো হলো—
১. নিম্ন উচ্চতাবিশিষ্ট ভূসংস্থানের কারণে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান নদী প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলো তাদের শাখা-প্রশাখা এবং উপনদীর সমন্বয়ে ঘন বিন্যস্ত নিষ্কাশন/প্রবাহ জালিকা গড়ে তুলেছে, যা বিস্তীর্ণ এলাকায় পানির প্রবাহ পৌঁছে দেয়।
২. উজানের দেশগুলিতে, নদনদীর উজান এলাকায় এবং দেশের অভ্যন্তরে ভারী বৃষ্টিপাত হয়।
৩. হিমালয় পর্বতে তুষার গলন এবং প্রাকৃতিকভাবে হিমবাহের স্থানান্তর ঘটে।
৪. পলি সঞ্চয়ন ও নদী ভাঙনের ফলে নদনদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া।
৫. নদীর পার্শ্বদেশ দখল হয়ে যাওয়া।
৬. প্রধান প্রধান নদীসমূহে একসঙ্গে পানি বৃদ্ধি ঘটে এবং নিষ্ক্রমণ সীমা অতিক্রম করে।
৭. জোয়ারভাটা ও বায়ুপ্রবাহের বিপরীতমুখী ক্রিয়ার ফলে নদনদীর সমুদ্রমুখী প্রবাহের গতির মন্থরতা (ব্যাক ওয়াটার ইফেক্ট) ঘটে।
৮. বিদ্যমান রেলপথ, সড়ক, মহাসড়ক পানি নির্গমন বাধার সৃষ্টি করে।
চিহ্নিত কারণগুলোর দুটি (৫ ও ৮ নম্বর) বাদে বাকিগুলো প্রাকৃতিক, শক্তিশালী এবং নিয়ামক (রেগুলেটিভ) কারণ। এগুলো পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। ৮ নম্বর কারণটি দূর করার চিন্তা করে লাভ নাই। বরং এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে এগোতে হবে। যে প্রয়োজন মেটাতে সড়ক, মহাসড়ক এবং রেলপথের পরিমাণ ও উচ্চতা ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকবে। বাকি থাকে ৫ নম্বর কারণটি। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী দখলমুক্ত হওয়ার পরিবর্তে দেশের নদ-নদী খাল বিল বরং ক্রমবর্ধমান হারে মানুষের দখলে চলে যাচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে ফ্যাপের পরামর্শ হলো অতিরিক্ত বন্যা প্রবণ এলাকায় পোল্ডার ও নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। বর্তমানে বাংলাদেশ বন্যার হাত থেকে জনবসতি ও ফসলি জমি রক্ষার জন্য প্রতিবছর ১ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর হারে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ (অধিকাংশই পোল্ডার) নির্মাণের কৌশল অনুসরণ করছে। এতে বাঁধের ভেতরে থাকা অঞ্চলকে রক্ষা করা গেলেও বাইরের অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ বাড়ছে বলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সারা দেশের সবগুলো নদীতে বাঁধ দিলেও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বলে নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না। কারণ উজান থেকে আসা পানি আমাদের তৈরি করা বাঁধের মধ্যে ঢুকতে বাধ্য নয়। বরং তা নিম্ন ঢালের বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে বিপুলভাবে প্লাবিত করে প্রবাহিত হয়ে যেতে কোনো বাধা নেই।
ফ্যাপ ১৯-এর পরামর্শ অংশে কাঠামোগত পদক্ষেপসমূহ ছাড়াও বন্যা প্রশমন প্রক্রিয়া ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের একটি বিকল্প কৌশল হিসেবে অকাঠামোগত পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে মত দেওয়া হয়েছে। ডিএফআইডি গবেষকদের মতে নিম্নভূমি অঞ্চলে বন্যার মতো বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার খুব কম ক্ষেত্রে সফলতা পেয়েছে। তাই সামাজিক অভিযোজনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার চিন্তা করা যেতে পারে। তাদের মতে পদক্ষেপগুলো হলো—
১. জনগণ যাতে দ্রুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে বন্যার পানির উচ্চতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সময় পূর্বে জনগণের কাছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে জোরদার করা।
২. নদনদীর উপচে পড়া পানি হ্রাসের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা সাধন। এ উদ্দেশ্যে বনায়ন এবং পুনর্বনায়নের সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ ও তার যথাযথ সংরক্ষণ করা যাতে পরিশোষণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে বন্যার পানির উচ্চতা হ্রাস ঘটতে পারে।
৩. ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন ও বিল্ডিং কোডের যথাযথ প্রয়োগ, শস্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ তথা, বন্যা প্রতিরোধী বা বন্যা সহনক্ষম শস্য চিহ্নিতকরণ ও রোপণ করা এবং শস্য রোপণ মৌসুমের অভিযোজন।
৪. প্লাবন ভূমিসমূহকে বিভিন্ন জোনে বিভক্ত করা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভূমি ব্যবহার জোন তৈরি করা।
 ছবি: প্রথম আলোযারা নিজে উপস্থিত থেকে বন্যা দেখেছেন বা নিদেনপক্ষে টিভির খবরে প্লাবিত অঞ্চলের চিত্র দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই এটা উপলব্ধি করেন যে এই বিশাল পানি প্রবাহের সঙ্গে কোনো প্রযুক্তি দিয়ে যুদ্ধ করে বা তার প্রবাহকে বাধা দিয়ে জেতা যাবে না। তবে কৌশল করে তার বিরূপতা থেকে বাঁচা যেতে পারে এবং বুদ্ধি খাঁটিয়ে সুবিধাও আদায় করা যেতে পারে। তার কিছুটা আমরা ইতিমধ্যে করেছি। বন্যা ও খরাকে পাশ কাটিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো গেছে কয়েক গুন। খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাংক বর্তমানে রোল মডেল হিসেবে দেখছে। ১৯৭০ সালে আমাদের ধানের উৎপাদন ছিল ১ কোটি ১০ লাখ টন। আবাদি জমির পরিমাণ ২০-৩০ শতাংশ কমে যাওয়ার পরও বর্তমানে ধানের উৎপাদন ৩ কোটি ২০ লাখ টনে পৌঁছেছে। সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান বিশ্বে তৃতীয় এবং চাল ও মাছ উৎপাদনে চতুর্থ। এ চিত্রটা আরও অন্যরকম হতে পারত। কৃষিজ উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকারি জিনিস হলো পানি। গঙ্গা ও তিস্তা থেকে ভারত পানি প্রত্যাহার করায় শুষ্ক মৌসুমে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল খরার কবলে পড়ে। শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষকদের ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভর করতে হয়। এতে উৎপাদন খরচ বাড়ে এবং কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উৎপাদন হয় না।
ছবি: প্রথম আলোযারা নিজে উপস্থিত থেকে বন্যা দেখেছেন বা নিদেনপক্ষে টিভির খবরে প্লাবিত অঞ্চলের চিত্র দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই এটা উপলব্ধি করেন যে এই বিশাল পানি প্রবাহের সঙ্গে কোনো প্রযুক্তি দিয়ে যুদ্ধ করে বা তার প্রবাহকে বাধা দিয়ে জেতা যাবে না। তবে কৌশল করে তার বিরূপতা থেকে বাঁচা যেতে পারে এবং বুদ্ধি খাঁটিয়ে সুবিধাও আদায় করা যেতে পারে। তার কিছুটা আমরা ইতিমধ্যে করেছি। বন্যা ও খরাকে পাশ কাটিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো গেছে কয়েক গুন। খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাংক বর্তমানে রোল মডেল হিসেবে দেখছে। ১৯৭০ সালে আমাদের ধানের উৎপাদন ছিল ১ কোটি ১০ লাখ টন। আবাদি জমির পরিমাণ ২০-৩০ শতাংশ কমে যাওয়ার পরও বর্তমানে ধানের উৎপাদন ৩ কোটি ২০ লাখ টনে পৌঁছেছে। সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান বিশ্বে তৃতীয় এবং চাল ও মাছ উৎপাদনে চতুর্থ। এ চিত্রটা আরও অন্যরকম হতে পারত। কৃষিজ উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকারি জিনিস হলো পানি। গঙ্গা ও তিস্তা থেকে ভারত পানি প্রত্যাহার করায় শুষ্ক মৌসুমে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল খরার কবলে পড়ে। শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষকদের ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভর করতে হয়। এতে উৎপাদন খরচ বাড়ে এবং কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উৎপাদন হয় না।
এ সমস্যার প্রথম সমাধান হলো ভারতের কাছে অভিন্ন নদীর যৌক্তিক পানি প্রবাহ আদায় করা। সেটা এখনো সম্ভব হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে হবে সেরকম কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে পানি প্রবাহের সবচেয়ে বড় উৎস ব্রহ্মপুত্র নদ। চীন সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ দিয়ে জল বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করেছে। ওপরের জলাধারের কিছু পানি তারা সেচ কাজের জন্য প্রত্যাহার করবে এ রকম শোনা যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে শুষ্ক মৌসুমে পানির সমস্যা আরও বাড়বে। সবগুলো অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা এমনকি স্বাভাবিক প্রবাহ পাওয়া গেলেই খরা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমন নয়। অতীতে নদীগুলোতে যখন বাঁধ ছিল না তখনো এই ভূখণ্ডে খরায় ফসলহানি এবং তা থেকে মঙ্গা ও দুর্ভিক্ষের অনেক উদাহরণ আছে। শুষ্ক মৌসুমে ফসল উৎপাদনের জন্য ষাটের দশকে সমন্বিত সেচ প্রকল্প গ্রহণের পর থেকেই মূলত অবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটতে শুরু করেছে।
আমরা প্রায়ই হা পিত্যেশ করি এই বলে যে পানির অভাবে বাংলাদেশ মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা সেরকম নয়। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মিঠা পানির প্রাপ্যতার হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীতে এক নম্বর। ব্রাজিলের রিজার্ভ ৪ হাজার ২৩৩ কিউবিক কিলোমিটার যা পৃথিবীতে সর্বাধিক। আমাদের রিজার্ভ ১ হাজার ২২৩ কিউবিক কিলোমিটার। ব্রাজিলের আয়তন বাংলাদেশের ৫৮ গুন। সেই হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ব্রাজিলের চেয়ে আমাদের পানির প্রাপ্যতা ৬.৭ গুন বেশি। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর রিজার্ভ ভারত ১ হাজার ৯১১ কিউবিক কিলোমিটার, চীন ২ হাজার ৮৪০ কিউবিক কিলোমিটার, পাকিস্তান ২৪৬ কিউবিক কিলোমিটার। রাশিয়ার আয়তন বাংলাদেশের ১১৫ গুন। তাদের রিজার্ভ ৪ হাজার ৫০৮ কিউবিক কিলোমিটার। বাংলাদেশের মাত্র সাড়ে তিন গুন। ২৮ দেশের সমন্বয়ে গঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রিজার্ভ ২ হাজার ৫৭ কিউবিক কিলোমিটার। বাংলাদেশের দ্বিগুণের কম। অস্ট্রেলিয়ার রিজার্ভ ৪৯২ কিউবিক কিলোমিটার, যা বাংলাদেশের রিজার্ভের অর্ধেকেরও কম। এই পরিসংখ্যান থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আমরা আসলে পানিতে ডুবে আছি, যদিও বছরের চার মাস দেশের একটা বড় অংশ পানি শূন্যতায় থাকে।
এবার দেখা যাক বন্যা এবং খরা সমস্যার যুগপৎ সমাধান কীভাবে হতে পারে। সারা পৃথিবীর পরিবেশবাদীরা বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ রুদ্ধ, নিয়ন্ত্রণ বা বিচ্যুত করার বিপক্ষে। প্রকৃতিকে যত স্বাধীন থাকতে দেওয়া যাবে তার কাছে তত বেশি ভালো ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবে এই তত্ত্বের চর্চা করার অবস্থায় আমরা নাই। জনপদ রক্ষায় যে বাঁধগুলো নির্মাণ করা হয়ে গেছে সেগুলো ধরে রাখতে হবে এবং এমনভাবে পুনর্নির্মাণ করতে হবে যে বড় বন্যায়ও যেন সেগুলো ধ্বংস না হয়। নতুন বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ যত বেশি বাঁধ নির্মাণ করা হবে পানি সাগরের দিকে প্রবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে তত বেশি বাধার মুখে পরবে এবং নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত করবে। গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (জি-কে প্রজেক্ট), ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) প্রকল্প, উপকূলীয় বেড়িবাঁধ প্রকল্প, উত্তরাঞ্চলে নলকূপ প্রকল্পের মতো বড় প্রকল্পগুলো চালু রাখার পাশাপাশি বন্যা প্রবণ এলাকার প্রত্যেক জনপদে উঁচু পাড়সহ একটা করে জলাধার খনন করতে হবে। বন্যার পানি জলাধারে ঢোকার পর স্লুইসগেট বন্ধ করে দিয়ে পানি ধরে রাখা হবে। জলাধার খননের সময় যে মাটি পাওয়া যাবে তা দিয়ে নিকটতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ উঁচু করে বন্যার পানির উচ্চতার ওপরে নিয়ে যেতে হবে। বন্যার সময় জনগণ তাদের বহনযোগ্য সম্পদ নিয়ে যাতে সেই মাঠে আশ্রয় নিতে পারে। এভাবে জীবন ও সম্পদহানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যাবে। জলাধারে মাছ চাষ ও হাঁস পালন করা যাবে। শুষ্ক মৌসুমে এই জলাধারের পানি দিয়ে এলাকার সেচের চাহিদা পূরণ হবে। এভাবে বাংলাদেশে বন্যা এবং খরা থেকে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সহনশীল পর্যায়ে নামিয়ে আনা যাবে; তবে নির্মূল করা যাবে না। এটা আমাদের ভৌগোলিক বাস্তবতা। এটা না মেনে ক্রমাগত কল্পনাবিলাসী পরিকল্পনা গ্রহণ করে যেতে থাকলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটার সম্ভাবনা থাকবে।


 Reporter Name
Reporter Name