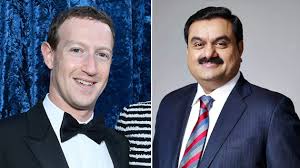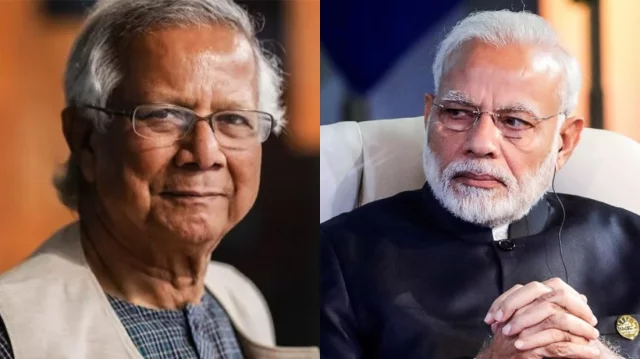ইদানীং লক্ষ্য করা যায়, এক শ্রেণির মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধ বলতে বোঝেন, ৭০-এর নির্বাচন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, অসহযোগ আন্দোলন এবং মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সশস্ত্র যুদ্ধ; অতঃপর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। জানার আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে দেখা যায়, এ প্রজন্মের অধিকাংশই স্বাধীনতার ইতিহাস বলতে এতটুকুই বোঝেন। এ জন্য এ প্রজন্মকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এ দোষ আমাদের। এটা আমাদেরই ভুল। অথবা আমরা হয়তো এটাই চাই। একটা দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের পথ ধরে বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয়েছে, সে ইতিহাস এ প্রজন্মের অনেকেই জানেন না। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, উনসত্তরের ১১ দফা ও গণ-আন্দোলনের মধ্যদিয়ে এদেশের মানুষ ধীরে ধীরে কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে এগিয়ে গেছে, তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব গণআন্দোলন কেমন করে জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল আমরাই কি তাদের জানতে দিচ্ছি?
বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা হয় মার্চ এবং ডিসেম্বরে স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের মাসে। স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন থাকে। এখানে চর্চা বলতে, স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা, সভা-সমাবেশ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নানা রঙের-নানা বর্ণের লেখালেখি এবং অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা বোঝানো হয়েছে। এসব আয়োজন আবার সাজানো হয় যে সরকার ক্ষমতায় থাকেন তাদের মর্জি মতো। ফলে এসব অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চিত্র সেভাবে উঠে আসে না। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরও মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমরা হাতে পাইনি। এ কারণে এ নিয়ে বিতর্কও পিছু ছাড়ছে না। যে যার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ এ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এ যুদ্ধেকে কোনো ধর্মের, কিংবা কোনো রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী তা বিবেচ্য বিষয় নয়। দেশ যখন অন্যের দখলে চলে যায়, জননী ও জন্মভূমির অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয়; তখন সমাজের সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করাই হয়ে ওঠে সব শ্রেণির মানুষের মূল উদ্দেশ্য। মুক্তিযুদ্ধের যে কোনো আলোচনায় জনগণের ভূমিকা বলতে প্রথমে আমরা সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কথাই বলে থাকি। তারপর আলোচনার চরিত্র কিছুটা বদলাতে থাকে। আলোচনায় চরিত্রের সংখ্যাও ক্রমাগত সীমিত হয়ে আসে অল্প কিছু রাজনৈতিক নেতা, কিছু সামরিক ব্যক্তিত্ব, কিছু বুদ্ধজীবী এবং আরও কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে। আমরা তখন ভুলে যাই, দেশটি কোনো ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর হাত ধরে শত্রুমুক্ত হয়নি। সমাজের সব শ্রেণির, সব ধর্মের এবং সব রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। এ কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। অথচ মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা যখন চলে, তখন আমাদের দুঃখবোধ হয় বৈকি।
এ ধরনের প্রচেষ্টার কথা আমরা মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকেই শুনে এসেছি। যুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসী সরকার এবং তখনকার কিছু প্রভাবশালী যুবনেতার রাজনৈতিক পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করে এ কথাই বলা যায়, একাত্তরের সেই দুর্বিসহ পরিস্থিতিতেও মুক্তিযুদ্ধকে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে গেছেন। বিশেষ করে প্রবাসী সরকারের সিদ্ধান্তের বাইরে যুবনেতাদের বিভিন্ন কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধকেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে দিয়েছিল। তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড অনেকের চোখেই ভালো ঠেকেনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। ভবিষ্যতেও যাতে নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক হানাহানি-ভাগাভাগি বজায় থাকে, এ রকম একটি সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই এরূপ সন্দেহের বীজ বপন করে দেওয়া হয়েছিল।
মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির যে কটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যায়। প্রথমেই প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে যে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল সে প্রসঙ্গে আসা যাক। তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে প্রবাসী সরকার গঠন করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি বাধা এসেছিল যুবনেতাদের কাছ থেকে। প্রবাসী সরকার গঠনে তারা ঘোর বিরোধী ছিলেন। কলকাতার গাজা পার্কের কাছে একটি বাড়িতে তখন শেখ মণি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ঘাঁটি করে থাকেন। ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে কলকাতা ফিরে আসেন। সেদিন সন্ধ্যায় ওই বাড়িতে যুবনেতারা ছাড়া আরও অনেকের সঙ্গে এএইচএম কামরুজ্জামান ও এম মনসুর আলীও ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে যে যে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তাজউদ্দিন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম তা সবাইকে অবগত করেন। এমন সময় ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলামকে পাশের একটি কক্ষে ডেকে নিয়ে শেখ মণি সরকার গঠনের প্রশ্নে অধিকাংশ এমপি, এমএলএ ও আওয়ামী লীগ সন্তুষ্ট নন জানান। সেদিন রাতেই লর্ড সিনহা রোডের একটি অফিসে পৃথক আরেকটি বৈঠক বসে। বৈঠকে কামরুজ্জামান, মিজানুর রহমান চৌধুরী, শেখ মণি, তোফায়েল অহমেদ ও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার লেখা বই ‘মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি’র ৪১ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ‘সেখানে শেখ মণি তার বক্তৃতায় বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শত্রু শিবিরে বন্দি, বাংলার যুবকরা বুকের তাজা রক্ত দিচ্ছে, এখন কোনো মন্ত্রিসভা গঠন করা চলবে না। মন্ত্রী-টন্ত্রী খেলা এখন সাজে না। এখন যুদ্ধের সময়। সকলকে রণক্ষেত্রে যেতে হবে। রণক্ষেত্রেই গড়ে উঠবে আসল নেতৃত্ব।’ তিনি যুদ্ধপরিচালনার জন্য একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করার কথাও বলেন। ১০ এপ্রিল শিলিগুড়িতে অন্য এক উপলক্ষ্যে শেখ মণি, তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে একা এক বৈঠকে প্রবাসী সরকার গঠন না করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করেন। তিনি আগরতলায় অবস্থিত এমপি, এমএলএ ও নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে, তাদের মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। আর এভাবে করা না হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলেও জানিয়ে দেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মণিকে বুঝিয়ে বলার সময় উলটো প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলামকে বলেন, ‘তারা (যুবনেতারা) বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অতএব, তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারও প্রশ্ন তোলা উচিত নয়।’ অথচ, সরকার গঠন করা না হলে ভারতও সাহায্যের হাত বাড়াতে পারছে না। সরকার গঠন ছাড়া সাহায্য করতে গেলে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমস্যা হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সরকার গঠনের ব্যাপারে ভারতের দিক থেকেও তাগাদা ছিল। শেষ পর্যন্ত প্রবাসী সরকার গঠিত হলো। কিন্তু যুবনেতারা তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তারা প্রবাসী সরকারের সম্পৃক্ততা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন। তাদের এ সিদ্ধান্ত দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত অটুট ছিল। শুধু তাই নয়, যুবনেতারা প্রবাসী সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে গেলেন।
বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ, মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয়ে সমন্বয়ের জন্য ভারত সরকার তিনটি কমিটি গঠন করেছিল। একটি রাজনৈতিক এবং অপর দুটি সামরিক। রাজনৈতিক কমিটির মাধ্যমে প্রবাসী সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। এ কমিটির প্রধান করা হয়, ডি পি ধরকে। যুদ্ধ প্রস্তুতি সংক্রান্ত কাউন্সিলের প্রধান করা হয় ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশকে। জেনারেল মানেকশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর তিনটি গোয়েন্দা বিভাগ এবং ভারতের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’কে অন্তর্ভুক্ত করে আরও একটি কমিটি গঠনে করেন যার চেয়ারম্যান করা হয় সেনাবাহিনীর উপপ্রধানকে। এ কমিটিকে যুদ্ধ প্রস্তুতির পাশাপাশি বাংলাদেশের তরুণদের নিয়ে একটি ‘বিশেষ বাহিনী’ গঠনের পরিকল্পনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়ে ‘র’-এর ওপর। বিশেষ বাহিনী গড়ার কারিগর হিসাবে পারদর্শী মেজর জেনারেল উবান ‘র’-এর পক্ষে এ কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব পান। তার জন্য কাজটি কঠিন হলেও তা অতি দ্রুত সহজ হয়ে গেল তাজউদ্দিন আহমদের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়াকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের চার যুবনেতার বিক্ষুব্ধ হওয়ার ঘটনায়। তাদের এ ক্ষোভের সুযোগ নেওয়া হলো। এভাবেই প্রবাসী সরকারের অগোচরে মুক্তিবাহিনীর সমান্তরাল ‘মুজিব বাহিনী’ গঠনের কাজ এগিয়ে চলে। জেনারেল উবান ভারত সরকারের বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ চার যুবনেতার সঙ্গে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করেন চিত্তরঞ্জন সুতারের কলকাতার ২১ নম্বর রাজেন্দ্র রোডের বাড়িতে।
মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকে আওয়ামী লীগ নেতাদের আশঙ্কা ছিল নদীর স্রোতের মতো যেভাবে বাঙালি তরুণ সমাজ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে প্রবেশ করছে, শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ না তাদের হাত থেকে ছুটে যায়। আওয়ামী লীগের চার যুবনেতাও তাই মনে করতেন। তাদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধটা ছিল একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ এবং যুদ্ধটা রাজনৈতিকভাবেই পরিচালিত করতে হবে, যাতে এর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই থাকে। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধের রিক্রুটমেন্ট যেন তাদের হাতেই থাকবে। রাজনৈতিক মটিভেশন তারাই দেবেন। সে মোতাবেক শুধু আওয়ামী লীগের এমপি, এমএনএ-রা আওয়ামী লীগের যুবকদের নির্বাচন করবে। প্রবাসী সরকারের এমন সিদ্ধান্তের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা সামরিক কর্মকর্তারা একমত পোষণ করতে পারেননি। এ বিষয়ে মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান তৎকালীন গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার কর্নেল ওসমানীকে বলেছিলেন, ‘স্যার এটা অত্যন্ত ভুল হবে। কারণ বহু যুবক, সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষক মজুর, ছাত্র-জনতা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে এসেছেন, যারা রাজনীতি করেন না। এই যে যারা দেশকে স্বাধীন করার জন্য এসেছেন, তাদের যুদ্ধে না নেওয়াটা হবে অত্যন্ত অন্যায়। এটা বরং যুদ্ধকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।’ উত্তরে সেদিন কর্নেল ওসমানী বলেছিলেন, ‘না, এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে-মন্ত্রিপরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এটাই সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।’ প্রবাসী সরকার শপথ নেওয়ার পর প্রথম যখন মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সব মন্ত্রী দেখা করতে দিল্লিতে যান তখন কর্নেল ওসমানী শুধু আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাসী যুবকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি প্রকাশ করেন। এ সময় রাজ্জাক ও তোফায়েল প্রস্তাব নিয়ে আসেন তাদের দায়িত্ব দিলে তারা ভালো ছেলে রিক্রুট করে দিতে পারে। ওসমানী তার পক্ষে তাদের রিক্রুট করার অধিকার দিয়ে একটি অথোরাইজেশন লেটার দিয়ে দিলেন। এ চিঠি যুবনেতাদের মুজিব বাহিনী গঠনে সহায়তা করেছিল বলে কথিত আছে।
বামপন্থিদের ব্যাপারে প্রবাসী সরকারের উৎকণ্ঠা ছিল আরও বেশি। মুক্তিযুদ্ধে প্রথম দিকে অভিযোগ ছিল বিভিন্ন সেক্টরে বামপন্থির বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের প্রশিক্ষণের কোনো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এ পর্যায়ে বামপন্থি নেতা কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন ও হায়দার আকবর খান রনো তাদের কর্মীদের মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষণের বিষয়ে সহযোগিতার জন্য প্রবাসী সরকারের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু সরকার, তাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি। মুক্তিবাহিনীতে বাম নেতাকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। যদিও সেপ্টেম্বর নাগাদ নানারকম সীমাবদ্ধতা ও আশঙ্কা সত্ত্বেও বামপন্থিদের মুক্তিযুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ বিষয়ে ভারত সরকারের একটি অংশ বামদের অংশগ্রহণে উৎসাহী ভূমিকা নেন। আওয়ামী লীগের যুবনেতারাও সতর্ক ছিলেন, যাতে বামপন্থিরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র হাতে না পায়। তারা ভারতীয় কর্তৃপক্ষকেও এ ব্যাপারে অনুরোধ করেন, অনেক অবাঞ্ছিত লোক, যারা বাংলাদেশে নকশালদের প্রতিরূপ, তারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ও অস্ত্র পাচ্ছে। তারা মুক্তিযুদ্ধে এগুলো ব্যবহার করবে না। স্বাধীনতা উত্তরকালের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখবে। বামপন্থিদের বিষয়ে তারা এতই সেন্সেটিভ ছিলেন যে বামপন্থিদের অনেক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে বন্ধও করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে ১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিক বীর উত্তম (বর্তমানে আওয়ামী লীগের এমপি)-একটি লেখায় নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছিলেন; ‘ভারতীয় এলাকার শ্রীনগর ফাঁড়ির কাছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওপর শুভপুর সেতুর অদূরে, ভাসানী ন্যাপের ব্যারিস্টার আফসার স্থানীয় বিএসএফ-এর সহযোগিতায় ছোট একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছিলেন। একটি জাতির জীবনে এমন ভয়াবহ দুর্যোগ মুহূর্তে কোন্ মুক্তিযোদ্ধা কোন্ পন্থি এটি নিয়েও প্রশ্ন উঠবে তা আমরা ভাবতেও পারিনি। …কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তি আমাদের এ সরলতাকে কর্তৃপক্ষের কাছে বিকৃতিভাবে উপস্থাপন করে এবং আমাদের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা চালায়। …ক্যাম্পটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কিছুটা হলেও অবদান রাখতে সক্ষম এটা অনুধাবন করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক চাপের কারণে ভারত সরকার ক্যাম্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।’
এত বাধাবিপত্তির পরও মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু থেমে থাকেনি। নানামুখী রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মাঝেও এ দেশের সাধারণ মানুষই লড়াই করে এ দেশকে শত্রুমুক্ত করেছেন। শত মতপার্থক্যকে তুচ্ছ করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশ কারও দয়া-দাক্ষিণ্যের দান নয় কিংবা কেউ একক শক্তিবলে এদেশকে স্বাধীন করে দেননি। লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের এ দেশ বাংলাদেশ। তাদের অবিস্মরণীয় সেই আত্মত্যাগের কথা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। এ কথা তাই বলতে হয়, মুক্তিযুদ্ধকে একচোখা ভাবে দেখলে ভুল হবে। মুক্তিযুদ্ধে সবার অবদানকে স্বীকার করে উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সব অপরাজনীতি বর্জন করে, এর বৈচিত্র্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। তাহলেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সবার কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে।
লেখক : কলামিস্ট
একেএম শামসুদ্দিন


 Reporter Name
Reporter Name